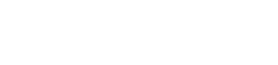Originally posted in বণিকবার্তা on 8 August 2025
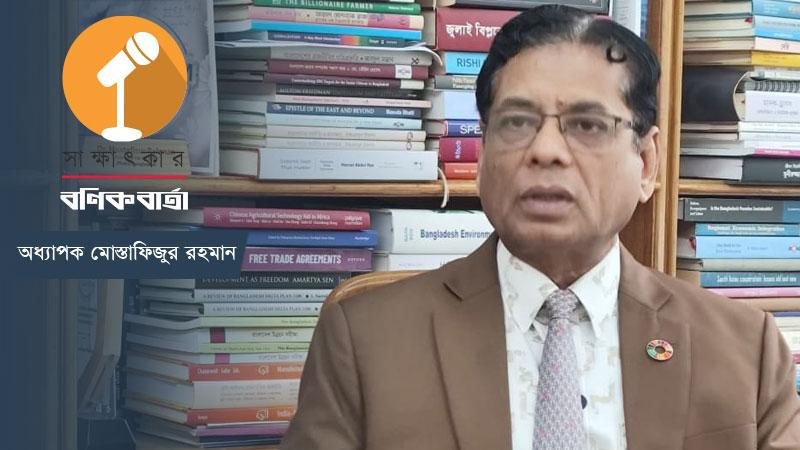
যে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকার দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছিল, সেটি মোকাবেলার একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু এ সরকারকে একই সঙ্গে রাজনৈতিক, ভূরাজনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন আকস্মিক সমস্যার সমাধানে কাজ করতে হয়েছে।
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো। বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ২৫ বছর শিক্ষকতা করেছেন। গবেষণাকর্মের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টির মর্যাদাপূর্ণ ইব্রাহিম স্মৃতি স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের বছরপূর্তিতে অর্থনৈতিক সংস্কার, বিনিয়োগ পরিস্থিতি ও সামষ্টিক অর্থনীতির চালচিত্র নিয়ে কথা বলেছেন বণিক বার্তায়। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সাবরিনা স্বর্ণা
অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের এক বছর পূর্ণ হয়েছে। এ সরকার দায়িত্ব নেয়ার সময় দেশের অর্থনীতি একপ্রকার খাদের কিনারে ছিল। সে জায়গা থেকে গত এক বছরে অর্থনীতিকে কতটা নিরাপদ জায়গায় আনতে পেরেছে বর্তমান সরকার?
যে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে অন্তর্বর্তী সরকার দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছিল, সেটি মোকাবেলার একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু এ সরকারকে একই সঙ্গে রাজনৈতিক, ভূরাজনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন আকস্মিক সমস্যার সমাধানে কাজ করতে হয়েছে। ফলে অর্থনীতির জন্য যে ধরনের মনোযোগ এবং অর্থনৈতিক বিভিন্ন সংস্কারের জন্য যে ধরনের গুরুত্ব দেয়া দরকার ছিল, সরকার সেই সুযোগ-সময় পুরোটা পায়নি। কিন্তু তার পরও সরকার চেষ্টা করেছে। কারণ জুলাই আন্দোলনের পেছনে বড় একটা যৌক্তিকতা ছিল অর্থনীতির তৎকালীন পরিস্থিতি—চাকরিপ্রত্যাশীদের কাজের প্রাপ্তিতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হচ্ছিল, শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার বেশি, আয়বৈষম্য, ভোগবৈষম্য, সম্পদবৈষম্য ছিল। অর্থনৈতিক কার্যকারণের ভিত্তিতে অসন্তোষ ছিল এবং এর সঙ্গে রাজনৈতিক-গণতান্ত্রিক অধিকারহীনতা সংযুক্ত হয়েই একটা গণ-অভ্যুত্থান হয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে আমি বলব যে অর্থনীতি যে জায়গায় ছিল সেখানে থেকে এখন বেশকিছু সূচকে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। অবশ্য বেশকিছু সূচক ঘিরে যে ধরনের প্রত্যাশা ছিল সে প্রত্যাশার প্রতিফলন আমরা পাইনি। বিশেষত মূল্যস্ফীতির হারে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসেনি।
গত বছরের জুলাইয়ে সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার সর্বোচ্চ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশ। সেটি বর্তমানে ৮ শতাংশের ঘরে নেমে এসেছে। ধারাবাহিক মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের মধ্যে বেশ অসন্তোষ রয়েছে। জনগণের ক্রয়ক্ষতার বড় অবনমন ঘটেছে। গত তিন বছরে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে সাধারণ মানুষের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জীবনমানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বর্তমানে মূল্যস্ফীতি কিছুটা সামাল দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু মূল্যস্ফীতির হার সামান্য কমলেও মূল্যস্তর ওপরেই রয়ে গেছে। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে যে ডিসেম্বরের মধ্যে ৬ শতাংশে এ হার নিয়ে আসবে। কিন্তু এ হার ৬ শতাংশে নেমে এলেও মূল্যস্তর ঊর্ধ্বমুখী থাকায় এরই মধ্যে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অবনমন হয়ে গেছে। এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার অন্যতম উপায় ছিল ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ চাঙ্গা করে কর্মসংস্থান তৈরি এবং শোভন আয়ের সৃষ্টি করা। কিন্তু সেটা হয়নি। মূল্যস্ফীতির হার বাগে আনতে গিয়ে আমরা সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির প্রচলন করলাম। আমাদের ব্যাংকের সুদের হার বর্তমানে অনেক বেশি। আমাদের অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক যেসব জায়গায় হাত দিয়ে কস্ট অব ডুইং বিজনেস (ব্যবসা ব্যয়) কমাতে পারতাম, সে জায়গাগুলোয় তেমন বড় পরিবর্তন হয়নি। ফলে আমরা দেখছি যে বিনিয়োগে চাঙ্গাভাব আসেনি।
মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে যদি ডিসেম্বর পর্যন্ত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বজায় রাখা হয়, তাহলে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থানের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়তে যাচ্ছে?
আমরা অতীত গবেষণায়ও দেখেছি বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির হার যখন ৪-৫ শতাংশ ছিল, তখনো বিনিয়োগে স্থবিরতা ছিল। সুতরাং মূল্যস্ফীতির হার নিচে নামিয়ে আনার জন্য আমাদের চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে। ব্যাংকে সুদের হার উচ্চস্তরে রয়ে গেছে। নীতি সুদহার আমরা কমাচ্ছি না। কিন্তু কেবল মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে আমরা বিনিয়োগে চাঙ্গাভাব আনব সেটাও কিন্তু না। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তারও এটার ওপর একটা অভিঘাত থাকে। তবে সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় ঘোষণা করেছেন। এ কারণে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলেই মনে করছি। কারণ অনেক বিনিয়োগকারী অপেক্ষা করছিলেন গণতান্ত্রিক উত্তরণের একটা নিশ্চয়তা পাওয়ার। উদাহরণ দিয়ে যদি বলি, কোন ধরনের সরকার আসবে, বর্তমান সরকারের সংস্কার কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা থাকবে কিনা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা কী রকম হবে, সুশাসনের অভাব যেটা একটা বড় কারণ ছিল দেশে বিনিয়োগবিমুখ হওয়ার সেক্ষেত্রে কোনো বড় পরিবর্তন আসবে কিনা।
এসবই নির্ভর করবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ওপর। কারণ এর হার কমলে নীতি সুদহার কমানো যাবে। তখন হয়তো ঋণের সুদের ওপর এটার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। কিন্তু আরো অনেক অনুঘটকের ওপর বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের বিষয়টি নির্ভর করবে। এরই মধ্যে আমরা দেখছি যে মূলধনি যন্ত্রপাতির আমদানি কমেছে ২৫ শতাংশ। উপরন্তু মূল্যস্ফীতির কারণে ব্যবসা ব্যয় বেড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বাণিজ্য-বিনিয়োগ সুশাসন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, দক্ষতা এগুলোর ওপরও নির্ভর করবে।
যেমনটি আপনি বলছিলেন, সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে সরকার অর্থনীতির অনেক বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেনি। সম্প্রতি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য সময়ও ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচিত সরকার আসার আগ পর্যন্ত বর্তমান সরকারের মনোযোগের বিষয়ে কী পরামর্শ দেবেন?
এখনো অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে বেশকিছু সময় আছে এবং সরকার যেসব পদচিহ্ন রেখে যাবে তা যদি ইতিবাচক হয় তাহলে পরবর্তী নির্বাচিত সরকারকে সেগুলো অব্যাহত রাখতে হবে। নয়তো জনগণের একটা চাপ নির্বাচিত সরকারের ওপর থাকবে। সুতরাং পার করে আসা সময়ে অন্তর্বর্তী সরকার যে ইতিবাচক পদক্ষেপগুলো নিয়েছে এবং সামনে যেগুলো তারা করতে পারবে সেটার একটা বড় ধরনের ইতিবাচক প্রভাব থাকবে বলে আমি আশা করি।
দেশের অর্থনীতির সংস্কারের বেশ ভালো কিছু উদ্যোগ আমরা এরই মধ্যে দেখেছি। বিশেষত বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ ভালো কয়েকটা উদ্যোগ নিয়েছে, যার মধ্যে একটি দুর্বল ব্যাংকগুলোকে একীভূতকরণ করার উদ্যোগ। এছাড়া যে ব্যাংকগুলোয় বিপুল অংকের ঋণখেলাপি হয়েছে, সেসব ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ড পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, সেজন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। খেলাপি ঋণের ক্ষেত্রে স্পষ্টতা আনা হয়েছে। অন্তত আমরা এখন জানতে পারছি যে ব্যাংকগুলোর প্রকৃত অবস্থা কী এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আরো ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। আশা করি, এ বিষয়গুলো সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক আগামীতেও অব্যাহত রাখবে। তারা এমন একটা জায়গায় এগুলো রেখে যাবে যেন নির্বাচিত সরকারও সেগুলো অব্যাহত রাখতে পারে। সেই সঙ্গে সেটাকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। জনগণের মধ্য থেকেও যাতে এসব কাজের জন্য চাপ থাকে।
পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার বিষয়ে কতটা অগ্রগতি হয়েছে?
দেশ থেকে পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনতে এখন পর্যন্ত আমরা বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। কিন্তু টাকা তো এখনো ফেরত আনা যায়নি। এটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু যেসব প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সেগুলোও চলমান রাখতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সম্মিলিতভাবে কাজ করে মামলা করা, মামলার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় আবেদন ইত্যাদি করেছে। তারপর আবার উচ্চ আদালতে অভিযোগ প্রমাণও করতে হবে। এসব প্রক্রিয়া এখনো শেষ হয়নি। তাই এগুলো চলমান রাখা জরুরি।
বিনিয়োগ চাঙ্গা করতে করণীয় কী হতে পারে?
কেবল বিনিয়োগ নয়, পাশাপাশি বাণিজ্য, বাজার ব্যবস্থাপনাসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো চাঙ্গা করা জরুরি। আমরা ওয়ান স্টপ সার্ভিস দেয়ার কথা বলছি। কিন্তু সেটি আমরা পারছি না। এক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমস্যা আছে। অবকাঠামতগত সমস্যার পাশাপাশি আমাদের দক্ষ শ্রমিকের অভাব আছে। আমরা ওয়ান স্টপ সার্ভিসের কথা বলছি, কিন্তু যদি গ্যাসের সরবরাহ না থাকলে কীভাবে ব্যবসায়ীকে গ্যাস দেব? সরবরাহ সক্ষমতা থাকলে হয়তো বলা যায় যে দ্রুত আপনাকে গ্যাসের জোগান দেব। এগুলো রাতারাতি সমাধান করা যায় না। কিন্তু অন্তত সমাধানের উদ্যোগ নেয়া যায়। যেমন আমাদের অফশোর-অনশোরে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য উদ্যোগ নেয়া দরকার। আমাদের জ্বালানি খাতে বেশকিছু ভালো উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। সেগুলোও অব্যাহত রাখতে হবে।
এছাড়া বিনিয়োগ পরিস্থিতি উন্নয়নে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল চালুর জন্য বেশকিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন শৃঙ্খলা বজায় থাকে। প্রয়োজনে প্রকল্পগুলো কাটছাঁটও করতে হবে। কারণ আমরা জানি, বিগত সময়ে প্রকল্পই ছিল দুর্নীতির বড় ক্ষেত্র। বর্তমানে এসব ক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিতে বেশকিছু পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। সেই পদক্ষেপগুলো আগামীতে এমনভাবে নীতি-নিয়মের মধ্যে স্থিত করতে হবে, যাতে পরবর্তী সময়ে যারাই দেশের দায়িত্ব নেবেন তারা একটা শৃঙ্খলার মধ্যে পড়তে বাধ্য হন।
কিন্তু হতাশার একটি জায়গা হলো, চলতি বছরের জন্য যে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে, সেটি খুবই গতানুগতিক হয়েছে। আগের বাজেটের গতানুগতিকতা থেকে বের হয়ে এসে আমরা যে নতুনভাবে চিন্তা করব, বাজেট বিন্যাস করব, সেটি হয়নি। সেটা করতে হলে আমাদের বেশকিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দ জিডিপির অনুপাতে বাড়াতে হলে কোন খাতগুলোয় কাটছাঁট করতে হবে সেটা মূলত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং অত সহজ সিদ্ধান্ত নয়। কিছু ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়ানো হলেও মূল্যস্ফীতির নিরিখে তা খুবই নগণ্য। কারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। এ বিষয়গুলোয় বড় ধরনের কোনো সংস্কার বা ধাক্কা যেটা আগামী বাজেটগুলোর জন্য একটা রেফারেন্স পয়েন্ট হয়ে থাকতে পারত, সেটা অন্তর্বর্তী সরকার করতে পারেনি।
এর বাইরে বাংলাদেশের জন্য আগামীতে একটা সমস্যা হয়ে থাকবে ঋণের বোঝা। আমাদের পুরো উন্নয়ন ব্যয় হয় অভ্যন্তরীণ ঋণ থেকে বা বৈদেশিক ঋণ দিয়ে। ফলে ঋণ পরিষেবার চাপ এখন আমাদের ক্রমান্বয়ে বাড়বে। তাই বাজেটের অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন। ঋণ যাতে কম নিতে হয় সেজন্য রাজস্ব বাজেটে উদ্বৃত্ত থাকতে হবে। তাই রাজস্ব খাতের সংস্কারে আরো জোর দেয়া আবশ্যক।
গ্যাস খাতের উন্নয়নের জন্য গঠিত তহবিলের অর্থ গ্যাস অনুসন্ধানের চেয়ে ঋণ হিসেবে ও রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বেশি দেয়া হয়েছে। সেই টাকা ফেরত আনা নিয়ে কিছু দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে গ্যাস অনুসন্ধান বা এ খাতের উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন সংকটের শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এটি সমাধানের উপায় কী?
এখানে পুরো বিষয়টাই হলো সরকারেরই একটা অংশের সঙ্গে আরেকটা অংশের বিবাদ। জ্বালানি খাতে আমাদের বড় ধরনের ব্যত্যয়ের জায়গা হলো, গ্যাস অনুসন্ধান না করে বিদেশ থেকে আমদানির জন্য আমরা এলএনজি ব্লকের কাছে আমরা জিম্মি হয়ে গেলাম। অফশোর-অনশোর কোথাও অনুসন্ধান করলাম না। আমরা সমুদ্র বিজয় করলাম কিন্তু যাদের বিপরীতে জয়ী হলাম, তারা সেখানে অনুসন্ধান করে গ্যাস উত্তোলন করছে। আর আমরা বিডিংই করতে পারিনি। এ জায়গাগুলোয় অগ্রাধিকার দেয়া হয় না। এখন চেষ্টা করা হচ্ছে এটা করার জন্য।
আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যে বিবাদ এখন হয়েছে সেটা সরকারকেই নিরসন করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় দরকার হবে। তবে আমি যেটা বুঝি সেটা হলো, আমাদের অর্থায়ন লাগবে। পেট্রোবাংলা, বাপেক্সের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। গ্যাস অনুসন্ধানকে আমাদের অবশ্যই অগ্রাধিকার তালিকার প্রথম তিনটির মধ্যে রাখতে হবে।