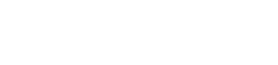Originally posted in কালেরকণ্ঠ on 7 August 2025
২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের সময় ঘোষণা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার আবহে একটি প্রয়োজনীয় অগ্রগতি। এত দিন নির্বাচন ঘিরে যে ধোঁয়াশা, গুজব ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিরাজ করছিল, এই ঘোষণার ফলে তা কিছুটা হলেও প্রশমিত হয়েছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যেকোনো দেশের জন্যই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগ পরিবেশের পূর্বশর্ত। তাই এই ঘোষণাকে আমরা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সম্ভাব্য সংকেত হিসেবে দেখতে পারি।
নির্বাচনের সুস্পষ্ট সময়সীমা ও কাঠামোর ধারণা পাওয়া গেছে, যা বিনিয়োগকারীদের পরিকল্পনায় সহায়ক হতে পারে। তবে এটি আস্থার একটি সূচনা মাত্র। পুরো আস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে প্রক্রিয়াটির বিশ্বাসযোগ্যতা, স্বচ্ছতা ও সহিংসতামুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। যদি সব রাজনৈতিক দলকে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করে, প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষ ভূমিকার মাধ্যমে একটি অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা যায়, তাহলে দেশি ও বিদেশি উভয় বিনিয়োগকারীর আস্থা জোরদার হবে।
অন্যদিকে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা বাড়লে এই ইতিবাচক পদক্ষেপের প্রভাব অনেকটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।
নির্বাচনের পূর্ববর্তী সময়ে বিনিয়োগ ও ব্যবসার গতি সাধারণত নির্ভর করে রাজনৈতিক ঝুঁকির মাত্রার ওপর। অভিজ্ঞতা বলে, বিনিয়োগকারীরা এই সময়টাতে অপেক্ষাকৃত সতর্ক থাকেন। বিশেষত দীর্ঘমেয়াদি ও বৃহৎ বিনিয়োগগুলো নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে থাকে।
কারণ সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নীতিগত ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। কর-নীতিতে হঠাৎ পরিবর্তন, রাজস্ব ব্যবস্থার রূপান্তর কিংবা বাণিজ্যিক বিধি-নিষেধ প্রভাব ফেলতে পারে বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে। যদিও কিছু স্বল্পমেয়াদি বাণিজ্যিক কার্যক্রম নির্বাচনকে ঘিরে বাড়তে পারে, সামগ্রিক বিনিয়োগচিত্র স্থবির থাকে।
সরকার বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে, আরো কিছু নীতিগত পদক্ষেপ নিতে হবে।
রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট, ব্যাংকিং দুর্বলতা, রপ্তানি সংকোচন, জলবায়ু ঝুঁকি ও নারীর প্রতি বৈষম্যের মতো বিষয়গুলোতে বাস্তবভিত্তিক অগ্রাধিকার দিতে হবে।
প্রথমত, নির্বাচনের আগে ও পরে অর্থনৈতিক নীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি প্রয়োজন।
দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে—বিশেষত শিল্পাঞ্চল ও বাণিজ্যিক এলাকায়।
তৃতীয়ত, ব্যাংকিং খাতের সুশাসন প্রতিষ্ঠা, ডলারসংকট নিরসন এবং রাজস্ব প্রশাসনের আধুনিকীকরণ করতে হবে।
এ ছাড়া ব্যবসা পরিচালনায় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস এবং ওয়ানস্টপ সার্ভিস কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন সময়োপযোগী পদক্ষেপ হবে।
নির্বাচনী ইশতেহার শুধু রাজনৈতিক আদর্শের দলিল নয়; বরং এটি দেশের উন্নয়ন কৌশল এবং অর্থনৈতিক রূপরেখার দিকনির্দেশক।
রপ্তানি খাতে বহুমুখীকরণ, আইটি, কৃষি-প্রক্রিয়াজাত পণ্য ও হালকা প্রকৌশলকে উৎসাহ দেওয়া, অবকাঠামো ও জ্বালানিতে টেকসই বিনিয়োগ, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জলবায়ু অভিযোজন—এসবই বাস্তবমুখীভাবে উপস্থাপন করতে হবে। তবে ইশতেহারে প্রতিশ্রুতি দিলেই হবে না, তার বাস্তবায়নের সময়সীমা ও কৌশলও নির্দিষ্ট করে জানাতে হবে। বিনিয়োগকারীরা শুধু প্রতিশ্রুতি নয়; বরং এর সম্ভাব্য বাস্তবায়ন পরিমাপ করেই আস্থা গড়ে তোলে।
সব মিলিয়ে বলা যায়, নির্বাচনের সময় ঘোষণা একটি শুভ সূচনা। তবে এই সূচনাকে ফলপ্রসূ করতে হলে নির্বাচনী পরিবেশে অন্তর্ভুক্তি, স্বচ্ছতা, নীতিগত ধারাবাহিকতা এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের স্পষ্ট অঙ্গীকার থাকতে হবে। তাহলেই এই রাজনৈতিক অগ্রগতি আমাদের কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার দিকে নিয়ে যেতে পারবে।
লেখক : নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)
অনুলিখন : মাসুদ রুমী