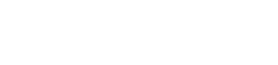Originally posted in DW বাংলা on 4 April 2025
পোশাক শিল্পের উত্থান ও শ্রমিকের প্রাপ্তি-বঞ্চনা
বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের যাত্রা শুরু আশির দশকে৷ সেই শিল্প আজ ৪০ বিলিয়ন ডলারের মতো রপ্তানি হচ্ছে৷ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানিমুখী শিল্পখাত৷

কিন্তু শিল্পের প্রসারের সমান্তরালে শ্রমিকদের অধিকারগুলো কি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে?
২০২১-২২ অর্থবছরে শুধুমাত্র তৈরি পোশাক শিল্প থেকে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪২ দশমিক ৬১৩ বিলিয়ন ডলার, যা বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ৮১ দশমিক ৮১ ভাগ৷ বর্তমানে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান ২য় এবং শীর্ষ স্থানে রয়েছে চীন৷
বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ি, গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৩৬ দশমিক ১৩ বিলিয়ন ডলারের৷ আগের ২০২২-২৩ অর্থবছরে যা ছিল ৩৮ দশমিক ১৭ বিলিয়ন ডলার৷ অর্থাৎ, একক শিল্প হিসেবে আজ গার্মেন্টস নিজের অবস্থান সুসংহত করেছে৷ কিন্তু আজকের এই অবদানের পেছনে যে লোকগুলো নিরলসভাবে কাজ করেছে তাদেরও রয়েছে নানা শোষণ ও বঞ্চনার গল্প৷ এখনও শ্রমিকের জীবনমানের তেমন উন্নতি হয়নি৷ নেই চাকরি শেষে বাকী জীবন ধারণের নিশ্চয়তা৷
পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ-র গত নভেম্বরের তথ্য অনুযায়ী, এই শিল্পে ১৯৮০ সালে নারী শ্রমিকদের হার ছিল ৮০ শতাংশ, যা ২০২১ সালে ৫৩ দশমিক ৭ শতাংশে নেমে এসেছে৷ মূলত ১৮ থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত তারা এই শিল্পে নিয়োজিত থাকেন৷ বয়স ৩৫ হওয়ার পর তারা এই কাজ ছেড়ে বিকল্প পেশার দিকে ঝুঁকতে থাকেন৷ এই শিল্পের সঙ্গে বর্তমানে ৪০ লাখেরও বেশি শ্রমিক প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত৷
শ্রমিক নেত্রী বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার সলিডারিটির প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক কল্পনা আক্তার ডয়চে ভেলেকে বলেন, “প্রথমে আমাদের দেখতে হবে গার্মেন্টসে নারীর অংশগ্রহণ কমে গেল কেন? আমাদের কারখানা মালিক, সরকার সবাই বড় বড় কথা বলছে যে, নারীর ক্ষমতায়ন করে ফেলল৷ তাহলে নারীরা চাকরি ছেড়ে যায় কেন? কারণ এই কারখানাগুলো নারী বান্ধব করতে পারেনি৷ টোটালি ফেল করেছে৷ গালিগালাচ থেকে শুরু করে সেক্সুয়াল হয়রানি সবকিছু আছে৷ এর সঙ্গে বেতনের বাইরে নারীদের দুইটা অধিকারকে যদি ধরেন৷ একটা মাতৃত্বকালীন ছুটি আরেকটা ডে কেয়ার সেন্টার৷ মাতৃত্বকালীন ছুটি চাইলে নারীকে আগে চাকরি হারাতে হবে৷ এখন অবশ্য পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে৷ কিছু কারখানায় মাতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া হয়৷ কিন্তু অধিকাংশ কারখানায় ডে কেয়ার সেন্টার নেই৷ ফলে একজন নারী শ্রমিক যখন পরিবার নিয়ে পরিকল্পনা করছে, তখন সে আর কাজে থাকতে পারছে না৷ কারণ সে এত বেশি বেতন পায় না যে, লোক রেখে বাচ্চাকে বড় করবে৷ এই কারণে নারীরা বেশি ঝড়ে পড়েছে৷ একজন নারী স্বপ্ন নিয়ে আসে, কিন্তু কিছুদিন পর সে একটা বেঞ্চমার্ক তৈরী করে ফেলে কতদিন সে চাকরি করবে৷”
তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশ৷ যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ), যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা ও নতুন বাজারে রপ্তানি বেড়েছে৷ এর মধ্যে যুক্তরাজ্য ও নতুন বাজার ছাড়া বাকি বাজারগুলোতে রপ্তানি বেড়েছে ১০ শতাংশের বেশি৷ চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাস অর্থাৎ জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে ১ হাজার ৯৮৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে৷ এই রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩ দশমিক ২৮ শতাংশ বেশি৷ গত অর্থবছর প্রথমার্ধে রপ্তানি হয়েছিল ১ হাজার ৭৫৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক৷
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-র পরিসংখ্যান দিয়ে তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ জানিয়েছে, চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে রপ্তানি হওয়া তৈরি পোশাকের অর্ধেকের গন্তব্য ছিল ইইউ৷ বড় এই বাজারে রপ্তানি হয়েছে ৯৮৭ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক৷ এই রপ্তানি গত অর্থবছরের তুলনায় ১৫ দশমিক ২২ শতাংশ বেশি৷ ইইউর দেশগুলোর মধ্যে জার্মানি, স্পেন, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, ইতালি ও ডেনমার্কে ৫০ কোটি ডলার বা তার বেশি পোশাক রপ্তানি হয়েছে৷ এর মধ্যে স্পেন ও ইতালি ছাড়া বাকি দেশগুলোতে রপ্তানি বেড়েছে ১০ শতাংশের বেশি৷
বিজিএমইএর তথ্যানুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে জার্মানিতে ২৪৭ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়৷ এই রপ্তানি গত অর্থবছরের তুলনায় ১৪ শতাংশ বেশি৷ এ ছাড়া স্পেনে ১৭০ কোটি, ফ্রান্সে ১০৯, নেদারল্যান্ডসে ১০৬, পোল্যান্ডে ৭৯, ইতালিতে ৭৭ ও ডেনমার্কে ৫৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে৷ এই দেশগুলোর মধ্যে পোল্যান্ডে তৈরি পোশাক রপ্তানি বেড়েছে সর্বোচ্চ ২৮ শতাংশ আর সর্বনিম্ন স্পেনে, ৩ শতাংশের কাছাকাছি৷
রাইজিং গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বিজিএমইএ এর সাবেক সহ-সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু ডয়চে ভেলেকে বলেন, “বাংলাদেশে গার্মেন্টস তো একদিনে এই জায়গায় পৌঁছেনি৷ এখানে সবার অবদান আছে৷ আশির দশকে যখন এটার শুরু হয় তখন কিন্তু আমাদের সক্ষমতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন ছিল৷ সেই চ্যালেঞ্জগুলো আমরা পার করেছি৷ এরপর যখন একটু ভালো করা শুরু করলাম তখন অনেকগুলো ইস্যু আমাদের সামনে এল৷ শিশু শ্রম বন্ধ করতে হবে৷ এরপর ২০০৪ সাল থেকে যখন কোটা উঠে গেল তখন আরেক ধরনের চ্যালেঞ্জ আসল৷ এরপর রানা প্লাজা বা তাজরিনের পর তিনটি ইস্যু বড় করে সামনে এল বিদ্যুৎ, অবকাঠামো এবং অগ্নিব্যবস্থা৷ এগুলোর পেছনে কিন্তু মালিকদের বিপুল অংকের টাকা খরচ করতে হয়েছে৷ এরপর আসল ফরেন কারেন্সি ইস্যু৷ বর্তমান সরকারের সময়ও আইন শৃঙ্খলা বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে সামনে এল৷ বায়াররা উদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমাদের অর্ডার দেওয়ার ক্ষেত্রে ভাবতে শুরু করলো সঠিক সময়ে আমরা ডেলিভারি দিতে পারবো কিনা? এই পরিস্থিতি উত্তরণের পর এখন আমার মার্কিন শুল্ক ইস্যু বড় আকারে আমাদের সামনে এসেছে৷ ফলে শুরু থেকে কখনোই মালিকরা স্বাচ্ছন্দে ব্যবসা করতে পারেননি৷ তারপরও নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আজকে এই জায়গায় এসেছে৷”
এত উন্নতির পরও শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নতি না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে সেন্টার ফর ওয়ার্কার সলিডারিটির প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক কল্পনা আক্তার ডয়চে ভেলেকে বলেন, “উত্তরণের পথ হচ্ছে, আমাদের মালিকদের যে কুমিরের কান্না সেটা বন্ধ করতে হবে৷ তাদের সব সময় নাই নাই৷ ডলারের দাম যখন ৬০ টাকা তখনও নাই, ডলারের দাম যখন ৮০ টাকা তখনও নাই এবং এখন যখন ডলারের দাম ১২২ টাকা এখনই নাই৷ অনন্ত গ্রুপের মালিক অনন্ত জলিল ঈদের আগে কুমিরের কান্না করে এখন তিনি পরিবার নিয়ে টোকিও ঘুরে বেড়াচ্ছেন৷ তার তো চৌদ্দগুষ্টির জমিদারি ছিল না৷ এই শ্রমিকদের ঘামের টাকায় তার কারখানায় কাজ করে যে মুনাফা এনে দিয়েছে সেটা দিয়েই তিনি পরিবার নিয়ে ঘুরছেন৷ তখন তিনি কি বললেন, ২০০ গ্রুপ ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে৷ মাথামোটা এই লোকটার কোন ধারণা নেই যে তিনি কি বলছেন৷ মূল কাথাটা হচ্ছে, লভ্যাংশ আপনি মালিক হিসেবে নেবেন৷ কিন্তু কত শতাংশ নেবেন? এখন ৮০ শতাংশ লভ্যাংশ আপনি নেওয়ার পর কিছু টাকা কাঁচামাল কেনার জন্য রাখবেন আর শ্রমিককে ২ শতাংশ দিতে গেলেই কুমিরের কান্না শুরু করেন যে, আমার টাকা নেই কোথা থেকে দেবো৷ এই ধরনের মানষিক অবস্থা থাকলে কিচ্ছু পরিবর্তন হবে না৷ মালিকরা যতক্ষন না মনে করবেন সামষ্টিকভাবে সবাই ভালো থাকলে তার কারখানা ভালো চলবে, ততদিন শ্রমিকের এই অবস্থার পরিবর্তন হবে না৷”
বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাত দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে পরিচিত৷ স্বল্প বেতনে দিন-রাত পরিশ্রম করলেও তাদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন৷ যদিও বাংলাদেশে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় আইন রয়েছে, বাস্তবে এই আইনগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না, ফলে শ্রমিকদের জন্য শ্রম আইন থেকে যে সুরক্ষা পাওয়ার কথা তা তারা পাচ্ছেন না৷ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ শ্রমিকদের কাজের সময়, বেতন, নিরাপত্তা, ছুটি, ক্ষতিপূরণ, এবং অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধারা নিয়ে গঠিত৷ এই আইনে গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকলেও বাস্তবে এসব বিধান অনেক ক্ষেত্রেই মানা হয় না৷ শ্রম আইনের ধারা ১০০ অনুযায়ী, একজন শ্রমিক দৈনিক সর্বাধিক ৮ ঘণ্টা কাজ করতে পারবেন৷ সপ্তাহে ছয় দিন কাজের পর একদিন ছুটি দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে৷ তবে বাস্তবে অনেক গার্মেন্টস শ্রমিককে দৈনিক ১০-১২ ঘণ্টা কাজ করতে হয়৷
গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জলি তালুকদার ডয়চে ভেলেকে বলেন, “আজকে যে গার্মেন্টস বাংলাদেশে এত বড় হয়েছে এর পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান সস্তা শ্রম৷ এই সস্তা শ্রমের কারণে আজকে মালিকরা এত বড় কারখানা করতে পেরেছেন৷ ফলে এখানে শ্রমিক শোষনটা তীব্র৷ শুরু থেকেই শ্রমিকরা ব্যাপক বঞ্চনার মধ্য দিয়ে এই শিল্পটা গড়ে তুলেছেন৷ মজুরীর জন্য তাদের সব সময় লড়াই করতে হয়েছে৷ এর বাইরেও ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার, যৌন হয়রানির বিরুদ্ধেও তাদের অনেক লড়াই করতে হয়েছে৷ ঘরে বাইরে শ্রমিকদের লড়াই করতে হয়েছে৷ ফলে তাদের বঞ্চনার মধ্য দিয়ে আজকে গার্মেন্টস সেক্টর এই জায়গায় পৌঁছেছে৷ এখনো সবচেয়ে কম মজুরি বাংলাদেশের শ্রমিকদের৷ খুবই সম্ভব ছিল শ্রমিকদের বেশি মজুরি দেওয়ার৷ মজুরি বাড়লে উৎপাদনশীলতাও বাড়ে৷ আমরা মনে করি, এখনো এই পরিবর্তনটা সম্ভব৷ বর্তমান সরকার যদি উদ্যোগ নেয়, তাহলে শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নতি হতে পারে৷”
সর্বশেষ পোশাক শ্রমিকদের নূন্যতম মাসিক বেতন ১২ হাজার ৫০০ টাকা নির্ধারণ করেছে মজুরি বোর্ড৷ টাকা নির্ধারণ করলেও অনেক কারখানায় শ্রমিকদের সেই পরিমাণ বেতন সঠিক সময়ে বা সম্পূর্ণ দেওয়া হয় না৷ বর্তমান জীবনযাত্রার ব্যয় ও মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির ফলে এ বেতনে তাদের মৌলিক চাহিদা মেটানো কঠিন হয়ে পড়েছে৷ বাংলাদেশ শ্রম আইনের ১৭৬ ধারা অনুযায়ী, শ্রমিকদের সংগঠনের অধিকার দিয়েছে এবং তাদের পক্ষ থেকে অধিকার দাবি করার সুযোগ রয়েছে৷ কিন্তু অনেক সময় শ্রমিকদের সংগঠনে অংশগ্রহণ করলে তাদের চাকরিচ্যুত করা হয় বা হুমকি দেওয়া হয়৷ ফলে তারা তাদের অধিকার দাবি করতে সাহস পান না৷
গার্মেন্টসের প্রবৃদ্ধি ঠিক রেখে শ্রমিকদের জীবনমানের কি আরেকটু উন্নতি করা যেতো কিনা জানতে চাইলে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-র সম্মানিত ফেলো ড. গোলাম মোয়াজ্জেম ডয়চে ভেলেকে বলেন, “এখানে তিনটি বিষয় দেখতে হবে৷ প্রথমত, শ্রমিকদের মজুরি, দ্বিতীয়ত, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ ও তৃতীয়ত, সংগঠন করার অধিকার৷ এখানে শ্রমিকদের মজুরি একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর পূনর্মূল্যায়ন করা হয়৷ রানা প্লাজা বা তাজরিনের ঘটনার পর কর্মপরিবেশ ভালো হয়েছে৷ কিন্তু তিন নম্বরে যেটা আছে সংগঠন করার অধিকার এটা একেবারেই উন্নতি হয়নি৷ এই কারণে আজকে শ্রমিকরা যে জীবনমান ধরে আছে, তার চেয়ে অনেক ভালো জীবনের সুযোগ তাদের ছিল৷ মজুরির ক্ষেত্রে আইনগত প্রক্রিয়ায় নিয়মিত বিরতিতে পূর্ণমূল্যায়ন করা হয়৷ যেটা ভালো দিক৷ কিন্তু পূনর্মূল্যায়নের সময় যে বিষয়গুলো দেখা উচিত সেগুলো কখনোই পূর্নাঙ্গভাবে বিবেচিত হয়নি৷ এখানে শ্রমিকদের মজুরি আরো বৃদ্ধির সুযোগ ছিল৷ আমরা যেটা বলে থাকি, একটা নূন্যতম মজুরি আরেকটা জীবনযাত্রার জন্য চলনসই মজুরি৷ সেই হিসেবে চলনসই মজুরির অনেক নীচে আমরা৷ আবার নূন্যতম মজুরি যেটা পেয়েছে, সেক্ষেত্রে আইনগতভাবে তার যা প্রাপ্য সেটা হয়নি৷ আমরা এমনও দেখেছি, শ্রমিকদের মজুরি ডলারের ভ্যালুতে কমেও গেছে৷ ১৯৯৩ সালে যে মজুরি ছিল, ২০০৬ সালের এসে যেটা করা হলো ডলারের ভ্যালুতে সেটা কমে গেল৷ এটা নেগোসিয়েশনের দুর্বলতার জন্য৷ কর্মপরিবেশ ভালো হলেও ট্রেড ইউনিয়নের জায়গায় তারা বরাবরই বঞ্চিত৷ ফলে তাদের পক্ষে নেগোসিয়েশনের ক্ষেত্রে বারবারই তারা বঞ্চিত হয়েছেন৷”