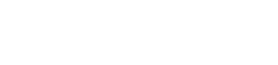Originally posted in প্রথম আলো on 26 July 2025
বর্তমানে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষ সমস্যার সমাধান করবে, নাকি নতুন ধরনের সমস্যার কারণ হবে, তা নিয়ে লিখেছেন খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম
অন্তর্বর্তী সরকারের অধীন ঐকমত্য কমিশনের চলমান রাজনৈতিক সংলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, দলপ্রধান, অধীন সরকার ও সরকারপ্রধানকে অধিকতর জবাবদিহির মধ্যে নিয়ে আসা। বিগত সংসদগুলোতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, দলপ্রধান ও সরকারপ্রধানের মাধ্যমে সরকার পরিচালনায় বিরোধী মতকে নিষ্পেষিত করে অকার্যকর সংসদ চালু রাখা হয়েছিল।
একটা কার্যকর সংসদের প্রত্যাশা দেশের রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজ, জনগণ—সবার। এই লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বিভিন্ন সংস্কার পদক্ষেপের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত হলো বর্তমান সংসদকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট করে একটি উচ্চকক্ষ তৈরি করা। এ ক্ষেত্রে যুক্তি হলো দ্বিকক্ষীয় সংসদের উচ্চকক্ষের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্যের মধ্যে রেখে সংখ্যাগরিষ্ঠতার অপব্যবহার বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া।
এ ধরনের একটি দাবি স্বাধীনতা–উত্তর কালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) উত্থাপন করেছিল, যা ১৯৮০ বা ১৯৯০–এর দশকেও দলটি তুলে ধরেছিল। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ৩১ দফার মধ্যে দ্বিকক্ষীয় সংসদের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করেছে।
সিপিডির (সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ) পক্ষ থেকে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, জাতীয় সংসদ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ গবেষকেরা বিভিন্ন সময়ে তাঁদের পরিচালিত গবেষণায় সংসদীয় ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অধীন সংসদের কার্যকারিতা হারানোর কারণ অনুসন্ধান করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্কারের সুপারিশ দিয়েছেন। কিন্তু সেসব সুপারিশে কখনোই দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ গঠনের সুপারিশ ছিল না।
এরই পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের ধারণাটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। এটা ঠিক, একটি পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে নতুন বাস্তবতায় নতুন ব্যবস্থার প্রত্যাশা থাকতে পারে। তবে প্রস্তাবিত উচ্চকক্ষ সমস্যার সমাধান করবে, নাকি নতুন ধরনের সমস্যার কারণ হবে, তা সম্যক উপলব্ধি করে সংসদীয় ব্যবস্থায় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন।
২.
বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলো সংসদে একক দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থায় জনগণের মতামত অগ্রাহ্য করার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করলেও এ সমস্যার উৎপত্তি বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণেই।
এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সংসদ অধিবেশনে কার্যকর আলোচনা না হওয়া, গুরুত্বপূর্ণ বিল পাসে সংসদ সদস্যদের ফ্লোর ক্রসিংয়ের সুযোগ না থাকা (৭০ ধারা), সংসদীয় কমিটিগুলোতে বিরোধী দলের সদস্যদের কমিটির প্রধান হওয়ার সীমিত সুযোগ রাখা, আর্থিক তদারকি কমিটিগুলোকে প্রায় অক্ষম করে রাখা, স্থায়ী কমিটিগুলোতে দায়সারা সভা আয়োজন করা ইত্যাদি বিষয় সংসদকে প্রায় অকার্যকর করে রেখেছে দশকের পর দশক।
■ উচ্চকক্ষ সৃষ্টি কোনো নতুন ফলাফল দেবে না, বরং এটা এক নতুন স্বার্থগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটাতে পারে, যা প্রচলিত কাঠামোকে আরও দুর্বল করবে।
■ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের যে কথা বলা হচ্ছে, তা অতিকেন্দ্রীভূত একটি রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হচ্ছে। রাষ্ট্রের এই অতিকেন্দ্রীকরণের সুরাহা হওয়া দরকার।
■ রাজনৈতিক দলগুলো যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিপদের কথা অনুভব করেছেন, সেটার সমাধান প্রয়োজন। তবে এ সমস্যার সমাধান এককক্ষীয় সংসদীয় ব্যবস্থায়ও করা সম্ভব।
এ ছাড়া গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর অনীহা, দীর্ঘসূত্রতা ও সংসদে তা রিপোর্ট না করা, সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্যের সুযোগ না থাকা, সংসদ পরিচালনায় কার্যবিধি সঠিকভাবে না মানা, দীর্ঘ সময় বিরোধী দলের সংসদ বর্জন করা, সংসদে প্রশ্নোত্তর/আলোচনা পর্বের গুরুত্ব না থাকা, প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলোআপ না হওয়া ইত্যাদি বিষয় অনেকাংশে দায়ী।
সংসদীয় ব্যবস্থার সংস্কারে প্রথমে এসব বিষয়কে প্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। আশার কথা, উল্লিখিত অনেক বিষয়েই ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় রাজনৈতিক দলগুলো ইতিমধ্যে একমত পোষণ করেছে।
৩.
কাঠামোগতভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারি দল হয়ে ওঠার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের ভোটাধিকারের অবমাননার উৎপত্তি সংসদে নয়। এর উৎপত্তি সংসদ ও স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর গণতন্ত্রায়ণের পথে অনাগ্রহ।
দলগুলো অনেকটাই অগণতান্ত্রিক পন্থায় জাতীয় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত নেতা নির্বাচন, নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরিবার, গোষ্ঠী, ধর্ম ইত্যাদির প্রাধান্য দেওয়া, দল পরিচালনায় অর্থায়নের সঠিক তথ্য গোপন রাখা, দলের পরিচালনায় অর্থ ব্যবহারের অস্বচ্ছতা, বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর কাছে থেকে আর্থিক সুবিধা নেওয়ার বিপরীতে অনৈতিক বা অবৈধ সরকারি সুবিধা দেওয়ার অঙ্গীকার করা এবং সরকার পরিচালনায় বিভিন্ন লবিং গ্রুপের অনৈতিক প্রভাব ইত্যাদি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির ভিত্তি কখনোই শক্তিশালী হতে দেয়নি।
দুর্ভাগ্যবশত, চলমান সংস্কার আলোচনায় এসব বিষয় নিয়ে তেমন কথা নেই। এমনকি রাজনৈতিক দলগুলোরও এসব বিষয় নিয়ে আলোচনার আগ্রহ নেই। মনে রাখা দরকার, বিদ্যমান কাঠামোতে রাজনৈতিক দল গঠন, দলনেতা নির্বাচন, দল পরিচালনা এবং দলের অর্থায়ন অপরিবর্তিত রেখে সংসদীয় ব্যবস্থায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বা দলপ্রধানের প্রভাব হ্রাস বা ক্ষমতার ভারসাম্য আনা সম্ভব নয়।
এ ক্ষেত্রে উচ্চকক্ষ সৃষ্টি কোনো নতুন ফলাফল দেবে না, বরং এটা এক নতুন স্বার্থগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটাতে পারে, যা প্রচলিত কাঠামোকে আরও দুর্বল করবে। পাকিস্তানের উচ্চকক্ষ ‘সিনেট’ এ রকম একটি উদাহরণ।
৪.
সংসদের উচ্চকক্ষের জন্য প্রস্তাবিত আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতি নিম্নকক্ষের প্রতিনিধিত্বের সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি থেকে তত্ত্বীয়ভাবে ভালো মনে হতে পারে। উভয় কক্ষের মধ্যে ‘নিয়ন্ত্রণ-ভারসাম্য’ বাড়ানোর জন্য তত্ত্বীয়ভাবে পিআর পদ্ধতি উপযুক্ত মনে হলেও বাংলাদেশের বাস্তবতা ভিন্ন।
সিপিডির বর্তমান গবেষণায় বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে, উচ্চকক্ষের ক্ষেত্রে, বিশেষত পিআর পদ্ধতির ক্ষেত্রে ছোট দলগুলোর আগ্রহ বেশি, যারা জনগণের ভোটে নির্বাচনে জয়ের সম্ভাবনা কম দেখে। অন্যদিকে বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো তাদের অপেক্ষাকৃত বয়স্ক নেতাদের জন্য উচ্চকক্ষকে নতুন সুযোগের অংশ হিসেবে দেখছে। কারণ, এই নেতাদের জাতীয় পর্যায়ে পরিচিতি থাকলেও মাঠপর্যায়ে নতুন বাস্তবতায় গ্রহণযোগ্যতা কম।
একই বিষয় সিভিল সোসাইটির কারও কারও ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এরা জাতীয়ভাবে পরিচিত, অথচ নির্বাচনের মাধ্যমে জিতে আসার সম্ভাবনা দেখেন না। তাঁদেরও দলীয় টিকিটে ‘বিশেষজ্ঞ’ ক্যাটাগরিতে উচ্চকক্ষে আসীন হতে আগ্রহ আছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।
দুর্ভাগ্যবশত উল্লিখিত ব্যক্তিদের কারও কারও পেশাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উচ্চকক্ষের জন্য তাঁরা যথেষ্ট উপযুক্ত বলে বিবেচিত হওয়ার কথা নয়। তাঁরা বিশেষজ্ঞ ক্যাটাগরিতে দায়িত্ব নিলেও মূলত দলীয় স্বার্থের বাইরে তেমন ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে মনে হয় না।
৫.
উচ্চকক্ষের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো নিম্নকক্ষে উত্থাপিত বিলের ওপর বিশেষজ্ঞ মতামত দেওয়া। পূর্বের সংসদগুলোয় দেখা গেছে, সংসদে উত্থাপিত প্রায় সব বিলই সরকারি দলের উত্থাপিত সরকারি বিল। বিগত সংসদগুলোতে বেসরকারি সদস্য বিল উত্থাপন খুব কম বা একেবারে অনুপস্থিত ছিল।
এর মূল কারণ, সরকারি দলের পক্ষ থেকে এ ধরনের বিল তুলতে নিজ দলের সদস্যদের নিরুৎসাহিত করা। এ ছাড়া বিরোধীদলীয় সদস্যদের জন্য বেসরকারি বিল প্রস্তুতের জন্য যে ধরনের কারিগরি সহায়তা থাকা দরকার, সংসদ সচিবালয়ে তার অনুপস্থিতিও একটি কারণ।
এ ক্ষেত্রে তল্পিবাহক বিরোধী দলগুলোও সরকারি দলের অনাকাঙ্ক্ষিত চাপ এড়াতে বেসরকারি বিল প্রস্তুত করতে ইচ্ছুক ছিল না। আগামী সংসদেও সরকারি বিলের ওপরেই আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে, এমনটা প্রতীয়মান হচ্ছে।
দুর্ভাগ্যবশত এসব বিলের ওপর তথ্য-উপাত্তভিত্তিক আলোচনা সংসদ সদস্যদের মধ্যে দু-একজন বাদে অধিকাংশের তেমন একটা করতে দেখা যায় না। বিলের ওপর ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে ৭০ ধারার খড়্গ থাকার কারণে সরকারি দলের সদস্যদের নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়া অসম্ভব।
এসব বিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো প্রস্তুত করে থাকে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে। এসব বিল কদাচিৎ সংসদীয় কমিটিতে আলোচনার জন্য পাঠানো হয়। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আসা সুপারিশের ভিত্তিতে খুব কম পরিবর্তনই করা হয়। সংসদে বিল পাসের ওপর আলোচনায় এসব সুপারিশ কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায়। অনেক সময় সরকারি এসব বিলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর চাহিদার প্রতিফলন থাকে।
এ থেকে প্রতীয়মান হয়, দলীয় মনোনয়নে নির্বাচিত উচ্চকক্ষের সদস্যরা তথাকথিত বিশেষজ্ঞ জ্ঞান বা দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে এসব বিলে খুব বড় ধরনের সংশোধনের সুপারিশের সাহস দেখাবেন না, অথবা সেসব সুপারিশ নিয়ে নিম্নকক্ষে খুব বেশি আলোচনা হবে বলে মনে হয় না।
এ ক্ষেত্রে বেসরকারি সদস্য বিল প্রণয়নের প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা দরকার। জাতীয় সংসদের ‘বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পার্লামেন্টারি স্টাডিস’কে সংসদ সদস্যদের জন্য শক্তিশালী জ্ঞানভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তোলা বিশেষ প্রয়োজন। এই ইনস্টিটিউট সংসদ সদস্যদের বিলসংক্রান্ত প্রস্তুতি, তথ্য–উপাত্ত প্রদান এবং খসড়া বিলের ওপর আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারবে।
৬.
দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদের যে কথা বলা হচ্ছে, তা অতিকেন্দ্রীভূত একটা রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হচ্ছে। রাষ্ট্রের এই অতিকেন্দ্রীকরণের সুরাহা হওয়া দরকার। স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতার ভাগাভাগি করা দরকার।
স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন এ ধরনের কিছু সুপারিশ করেছে। সেটা হলে সংসদ সদস্যদের কিছুটা হলেও সংবিধান প্রস্তাবিত কাজের দিকে (আইন প্রণয়ন) অধিক মনোযোগী করা সম্ভব হবে।
৭.
একটি দ্বিকক্ষীয় সংসদ গঠন করার জন্য যে ন্যূনতম বৈচিত্র্য প্রয়োজন, বাংলাদেশ কোনো বিচারেই সেটার জন্য উপযুক্ত নয়। সাধারণত দ্বিকক্ষীয় সংসদ গঠনের ক্ষেত্রে ফেডারেল সরকারকাঠামো, বৃহদায়তনের দেশ, ভৌগোলিক বৈচিত্র্য, ভাষাগত বৈচিত্র্য, ধর্ম বা গোষ্ঠীগত বৈচিত্র্য ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য নয়।
ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান, পূর্ব বাংলা বা বঙ্গ নামের অঞ্চলটি) একটি সমজাতীয়, সমপ্রকৃতির অঞ্চল হিসেবে আইনগতভাবে স্বীকৃত হয়ে এসেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে—সুদীর্ঘ ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে, ব্রিটিশ ভারত ও পাকিস্তানি উপনিবেশকাল পর্যন্ত। এর ফলে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনকালে এককক্ষীয় পার্লামেন্ট প্রচলনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
ঐতিহাসিক বিচারেও দ্বিকক্ষীয় সংসদের দাবিটি বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ধোপে টেকে না। বেশ কিছু ছোট দেশে দ্বিকক্ষীয় ব্যবস্থা চালু রয়েছে (নেপাল, ভুটান), তার মানে এই নয় যে বাংলাদেশে এ রকম কাঠামোর চাহিদা রয়েছে।
৮.
এটা সত্যি, রাজনৈতিক দলগুলো যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিপদের কথা অনুভব করেছে, সেটার সমাধান প্রয়োজন। তবে এ সমস্যার সমাধান এককক্ষীয় সংসদীয় ব্যবস্থায়ও করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সংসদ–সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ, সংসদীয় প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ এবং রাজনৈতিক দলগুলোতে অধিক গণতন্ত্রায়ণের অঙ্গীকার ও উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।
বর্তমান সংসদীয় কাঠামোকে শক্তিশালী করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আধিপত্য হ্রাসে ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলো কিছু ঐকমত্যে পৌঁছেছে। এর মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় বাদে সংসদ সদস্যদের ফ্লোর ক্রসিং অনুমোদন দেওয়া, নারী সংসদ সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্তকরণ, প্রধানমন্ত্রীর সময়কাল সীমিত করা, প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধান একই ব্যক্তি না হওয়া ইত্যাদি।
তবে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে জবাবদিহির মধ্যে রাখার ক্ষেত্রে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে আর্থিক তদারকি–সংক্রান্ত কমিটিগুলোকে শক্তিশালী করা, সংসদ পরিচালনায় কর্মপ্রণালি কঠোরভাবে মেনে চলা, সংসদীয় কমিটিগুলোর কার্যক্রমের নিয়মিত মূল্যায়ন করা, স্পিকারের সভাপতিত্বে পরিচালিত কমিটিগুলোকে শক্তিশালী করা এবং সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষজ্ঞ মতামত নেওয়া।
সিপিডির গবেষণায় দেখা গেছে, সংসদীয় কার্যক্রমের নিয়মিত মূল্যায়নের জন্য একটি স্বাধীন ‘ওয়াচ ডগ’ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এ কমিশন সংসদীয় কার্যক্রম, সাংবিধানিক কার্যক্রম ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের ওপর নিয়মিত মূল্যায়ন করবে। এ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় আইনি কাঠামোতে প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক কমিশন যা ‘ভেনিস কমিশন’ নামে পরিচিত, সে রকম একটি কমিশনের আলোকে বাংলাদেশের জন্য উপযুক্ত পার্লামেন্টের অধীন স্বাধীন কমিশন গঠন করা যেতে পারে। সিপিডি বর্তমানে এ কমিশনের কাঠামো ও কার্যক্রমের আওতা নিয়ে কাজ করছে।
ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম গবেষণা পরিচালক, সিপিডি