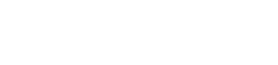Originally posted in প্রথম আলো on 24 April 2025
ফিরে দেখা—৭: সরকারি প্রতিষ্ঠান
কারখানাগুলো উৎপাদনমুখী করতে পারছে না বিটিএমসি
বন্ধ ২৫টি বস্ত্র কারখানা আবার চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয় ২০১৪ সালে। এ পর্যন্ত মাত্র ৩টিতে উৎপাদন শুরু হয়েছে।
এক যুগের চেষ্টায় বন্ধ থাকা ২৫ কারখানার মধ্যে মাত্র একটিতে পুরোদমে উৎপাদন শুরু হয়েছে। দুটিতে শুরু হয়েছে আংশিক উৎপাদন। বাকি কারখানাগুলোকে কবে নাগাদ উৎপাদনমুখী করা সম্ভব হবে, তা–ও নিশ্চিত নয়। এতে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার যেমন হচ্ছে না, তেমনি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হওয়াসহ আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে।এ চিত্র বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশনের (বিটিএমসি)।
বিটিএমসির নথিপত্র ঘেঁটে দেখা যায়, করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণে থাকা ২৫টি বস্ত্র কারখানার উৎপাদন ১৯৯৭ সালে বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৪ সালে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে গিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কারখানাগুলো চালু করার নির্দেশনা দেন। এর ধারাবাহিকতায় ১৬টি কারখানা পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) পদ্ধতিতে পরিচালনার জন্য অর্থনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (সিসিইএ) নীতিগত অনুমোদন দেয়।
পিপিপি প্রকল্পসমূহের দপ্তর ১৭ এপ্রিল প্রথম আলোকে জানায়, ১৬টি কারখানার মধ্যে ৪টি পিপিপির আওতায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এর মধ্যে পূর্ণ উৎপাদনে রয়েছে ঢাকার ডেমরার আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড। আংশিক উৎপাদনে গেছে রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড। আর পিপিপির বাইরে থাকা বিটিএমসির নারায়ণগঞ্জের চিত্তরঞ্জন কটন কারখানার জায়গা প্লট আকারে বিক্রি করা হচ্ছে। সেখানে বিক্রি হওয়া ১০টি প্লটের ৩টিতে উৎপাদন শুরু হয়েছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এ ৩টি ছাড়া ২২টি কারখানা উৎপাদনে যেতে পারেনি।
বিটিএমসির প্রকল্প পরিচালক (পিপিপি প্রকল্পসমূহ) কাজী ফিরোজ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, পিপিপি প্রকল্পগুলোয় অনেক অংশীজন রয়েছে—বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পিপিপি কর্তৃপক্ষ। সব আইনি প্রক্রিয়া মানতে গিয়ে সময় লাগে। বিটিএমসির সব কারখানা উৎপাদনমুখী করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
ছাড় দিয়েও কিস্তি পাচ্ছে না
পিপিপির আওতায় এ পর্যন্ত চারটি কারখানা দিয়েছে বিটিএমসি। প্রথম দেওয়া হয় আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইলকে। ২০১৯ সালের ২৫ জুন করা চুক্তি অনুযায়ী ৩০ বছরের জন্য কারখানাটি পেয়েছে তানজিনা ফ্যাশন। তবে প্রথম তিন বছর ছিল গ্রেস পিরিয়ড। এর মানে বিটিএমসিকে মাসিক যে অর্থ দেওয়ার কথা, এ তিন বছর তা দিতে হবে না। করোনা অতিমারির কারণে আরও দুই বছর ছাড় দেয় বিটিএমসি। তবে এরপরও বিটিএমসিকে মাসিক অর্থ পরিশোধ করছে না তানজিনা ফ্যাশন।
২০১৯ সালের ২১ জুলাই করা চুক্তির আওতায় টঙ্গীর কাদেরিয়া টেক্সটাইলকে ওরিয়ন গ্রুপের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তিন বছরের গ্রেসসহ ৩০ বছরের জন্য কারখানাটি দেওয়া হয়। করোনার কারণে ওরিয়ন গ্রুপকেও দুই বছরের অর্থছাড় দেওয়া হয়। তারাও ছাড়ের পাঁচ বছর পেরোনোর পর মাসিক অর্থ পরিশোধ করছে না।
জানা গেছে, কারখানা দেখিয়ে ব্যাংকঋণ নেওয়ার সুযোগ না থাকায় উৎপাদনে যেতে পারেনি ওরিয়ন গ্রুপ। এ অবস্থায় উৎপাদনে না যাওয়া এবং মাসিক অর্থ পরিশোধ না করায় যে সংকট তৈরি হয়েছে, তা মন্ত্রণালয়, বিটিএমসি ও পিপিপি কর্তৃপক্ষ সমন্বিতভাবে সমাধানের চেষ্টা করছে বলে পিপিপি প্রকল্পসমূহের দপ্তর জানিয়েছে।
আহমেদ বাওয়ানী কারখানায় উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছে তানজিনা ফ্যাশন। মাসিক অর্থ পরিশোধের বিষয়ে সম্প্রতি তারা বিটিএমসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করেছে।
প্রাণ–আরএফএল গ্রুপ গত ডিসেম্বরে পিপিপির আওতায় দুটি কারখানা নিয়েছে—চট্টগ্রামের আর আর টেক্সটাইল ও রাজশাহী টেক্সটাইল। এর মধ্যে রাজশাহী টেক্সটাইলে উৎপাদনে গেছে। উৎপাদনে যাওয়ার প্রক্রিয়া চলছে আর আর টেক্সটাইলে। তিন বছর গ্রেস পাওয়ায় কারখানা দুটির জন্য এখনো মাসিক অর্থ দিতে হচ্ছে না প্রাণ–আরএফএলকে।
পিপিপি প্রকল্পসমূহের দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, পিপিপির আওতায় থাকা ৯টি কারখানার দরপত্র আহ্বানের জন্য কার্যক্রম চলছে। চট্টগ্রামের জলিল টেক্সটাইল কারখানা ও সাভারের আফসার কটন কারখানা নিয়ে মামলা চলছে। আর ফেনীর দোস্ত টেক্সটাইল কারখানার দরপত্র আহ্বানের পর তা মূল্যায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।
অন্য কারখানাও উৎপাদনের বাইরে
সম্প্রতি ওয়েস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাছে কুড়িগ্রাম টেক্সটাইল, লয়েল টেক্স লিমিটেডের কাছে চট্টগ্রামের ভালিকা উলেন এবং ফাস্ট আইকন লিমিটেডের কাছে সিলেট টেক্সটাইল কারখানা ৩০ বছরের জন্য ভাড়া দিয়েছে বিটিএমসি। এসব কারখানা এখনো উৎপাদনে যেতে পারেনি।
খুলনা টেক্সটাইলে পার্ক, রিসোর্ট, বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স করার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ঈগলস্টার, কোকিল ও কিশোরগঞ্জ টেক্সটাইল কারখানা নিয়ে মামলা চলছে।
জানা যায়, ১৯৭২ সালে ৭৪টি বস্ত্রকল নিয়ে গঠিত হয় বিটিএমসি। এরপর আরও ১২টি বস্ত্রকল স্থাপন করা হয়। বিটিএমসির কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৬। তবে ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সময়ে বিটিএমসি ২৫টি কারখানা রেখে ৫৮টি বিক্রি, হস্তান্তর ও অবসায়ন করে এবং ৩টি কারখানা নামসর্বস্ব।
বিটিএমসির শ্রমিক ও কর্মচারীদের মালিকানা দিয়ে ৯টি কারখানা হস্তান্তর করা হয়েছে। সেগুলোর একটি ঢাকা কটন মিল। কারখানাটির একজন কর্মকর্তা জানান, কারখানার সব যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গেছে। ভবনও ভেঙেচুরে গেছে। ফলে উৎপাদনে যাওয়ার সুযোগ নেই। কারখানার বিভিন্ন অংশ বিটিএমসির সাবেক কর্মচারী ও শ্রমিকেরা ভাড়া দিয়েছেন।
ঢাকা কটনের মতো শ্রমিক-কর্মচারীদের কাছে হস্তান্তর করা বাকি আটটি কারখানাও উৎপাদনে নেই। বিটিএমসির কর্মকর্তারা জানান, এগুলোও উৎপাদনে না থাকায় কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে না, দেশেরও কাজে আসছে না।
বিটিএমসির মতো সরকারের বিভিন্ন করপোরেশনের অধীন থাকা কারখানাগুলো পরিচালনার জন্য সমন্বিত কৌশল প্রণয়ন দরকার বলে মনে করেন বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সিপিডির বিশেষ ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, এসব কারখানার পেছনে সরকারের খরচ আছে। কিন্তু সেভাবে রিটার্ন আসছে না। কোনটা বেসরকারীকরণ করা হবে, কোনটার ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন করা হবে, কোনটা লিজ দেওয়া হবে বা অন্য শিল্পের জন্য অবকাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত হবে—এসব পর্যালোচনা করে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান বের করা দরকার।