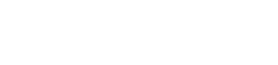Originally posted in দেশ রূপান্তর on 26 October 2025
বৃৃহত্তর সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সরকার অনেকগুলো সংস্কার কমিশন করেছিল। এগুলো ছিল ইতিবাচক পদক্ষেপ। তার মধ্যে শ্রম সংস্কার কমিশনকে অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। অন্তর্বর্তী সরকার যেসব বিষয়ে শুরু থেকে গুরুত্ব দিয়ে আসছিল, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শ্রমিকদের অধিকার, কর্মস্থলের নিরাপত্তা ও যুগোপযোগী শ্রম আইন প্রণয়ন। সরকারের নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এসব বিষয় দৃশ্যমান হয়েছে। এ ছাড়া যেসব দেশের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, তাদের তরফ থেকেও শ্রম সংস্কার ও শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যবিষয়ক যে দরকষাকষি হয়েছে, সেখানে ট্যারিফের বাইরে অন্যান্য যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে শ্রম সংস্কারের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। সেই বিবেচনায় শ্রম সংস্কারের জন্য একটি কমিশন গঠন এবং সেই কমিশনের প্রতিবেদন একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছে। এরই মধ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন তাদের প্রতিবেদন সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। প্রতিবেদনে শ্রমসংক্রান্ত প্রায় সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কী ধরনের সংস্কার দরকার, সে বিষয়ে সিপিডির পক্ষ থেকে স্বাধীনভাবে পর্যালোচনা ও সুপারিশ তুলে ধরা হয়। সিপিডি ৮টি বিষয়ের ওপর সুপারিশ দিয়েছিল। এগুলোর প্রতিটির ক্ষেত্রে কী ধরনের আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও কার্যক্রমগত সংস্কার দরকার হবে সে বিষয়ে সিপিডি সুপারিশ দিয়েছে। শ্রম সংস্কার কমিশন সেখান থেকে বেশ কিছু সুপারিশ গ্রহণ করেছে।
অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য প্রথমে ৬টি কমিশন গঠন করে। পরবর্তী সময়ে আরও ৮টি কমিশন গঠন করা হয়। এর বাইরে কিছু কমিটি গঠন করা হয়েছে। যার সবগুলোর ভবিষ্যৎ মোটামুটি একই রকম। বর্তমানে সরকারের মূল যে গুরুত্বের বিষয়গুলো রয়েছে, এসব কমিশন তার বাইরে অবস্থান করছে। সরকার যে ঐকমত্য কমিশন গঠন করেছে সেখানে সরকারের প্রথম দিকে উত্থাপিত সংবিধান সংস্কার, সংসদীয় সংস্কার, নির্বাচন সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে কার্যপরিধি সাজানো হয়েছে। এসব সংস্কারের বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য যেসব কমিশন গঠন করা হয়েছিল, সেগুলোর অগ্রগতি এক ধরনের পর্যালোচনামূলক কার্যক্রমের মধ্যে আটকে গেছে। অর্থাৎ কমিশনের প্রতিবেদনের আলোকে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থা সে বিষয়ে পর্যালোচনামূলক কার্যক্রমের মধ্যে আটকে আছে। অর্থাৎ কমিশনের সুপারিশের আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সেগুলোর বাস্তবায়নের বিষয়ে উদ্যোগ থমকে যায়। অতীতেও তা লক্ষ করা গেছে। নাগরিক সমাজ বা কোনো কমিশনের সুপারিশমালা প্রায়োগিকভাবে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে, মন্ত্রণালয়গুলোর পক্ষ থেকে যে ধরনের উদ্যোগ নেওয়া দরকার সে বিষয়ে ঘাটতি লক্ষ করা যায়। আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, কমিশন তাদের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলো কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং এসব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কী ধরনের করণীয়, সে বিষয়ে আলোচনা হয়।
সুপারিশের আলোকে যেসব সংস্কার হওয়া দরকার তার দু-একটি বিষয়ে কিছু অগ্রগতি হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অগ্রগতি দৃশ্যমান নয়। শ্রম সংস্কারের ক্ষেত্রে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বার্ষিক সম্মেলনে বাংলাদেশকে শ্রমক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কিছু শর্ত শিথিল করতে বলা হয়েছিল। এক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনে কিছু পরিবর্তন আনা দরকার। এর পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান আইনে কোনো কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করতে হলে, ৩০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতি থাকার যে বিধান রয়েছে, সেখানে পরিবর্তন আনার সুপারিশ করা হয়। এক্ষেত্রে শ্রমিকের শতাংশের হিসাবের পরিবর্র্তে, কারখানার আকার নির্বিশেষে কমপক্ষে ২০ জন শ্রমিক সম্মতি দিলেই সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। শ্রম সংস্কার কমিশন এ বিষয়ে নির্দিষ্ট সুপারিশ দিয়েছে। প্রতিবেদনটি আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে (আইএলসি) উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াগত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে বিষয়টি আলোচনার টেবিলে আসার পর, মালিকপক্ষের তরফ থেকে কিছু ভিন্নতম তুলে ধরা হয়। তাদের বক্তব্য ছিল, এত অল্পসংখ্যক শ্রমিকের সম্মতিতেই যদি ট্রেড ইউনিয়নের সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে যে কোনো ধরনের কারখানাতে ট্রেড ইউনিয়ন করতে হবে। সেক্ষেত্রে কোনো কারখানার সক্ষমতা বিবেচনায় নেওয়া হবে না। এতে ছোট কারখানাগুলো সমস্যায় পড়তে পারে। এ বিষয়ে কিছুটা পরিমার্জন করে সুপারিশ চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। আইএলওর তিনটি কনভেনশন অনুস্বাক্ষরের বিষয়ে সরকার, নীতিগতভাবে একমত হয়েছে বলে গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে। স্বভাবতই শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশের সঙ্গে, এর একটি সামঞ্জস্য আছে। সিপিডির পক্ষ থেকে যে সুপারিশ দেওয়া হয়েছিল, সেখানে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তার বিষয়ে একজন স্থায়ী কর্মকর্তাকে কারখানায় নিয়োগ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। এর বাইরে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করার সুপারিশ করা হয়েছে। কারণ এক্ষেত্রে অস্পষ্টতা আছে। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে নির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরির সুপারিশ করা হয়েছে। পাশাপাশি কারখানার বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিতের বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। আর এসব কমপ্লায়েন্স সঠিকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না সে বিষয়ে ভিজ্যুয়াল প্রামাণিক তৈরি করতে হবে শুধু টিক চিহ্ন দিলে হবে না। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য তদারকির বিষয়টি ইপিজেডের কারখানাগুলোতে অনুমোদন করতে হবে। দেশে ইপিজেডের জন্য একটি পৃথক আইন রয়েছে। আইনটি প্রণীত হয় ১৯৮০ সালে। সে সময়ের বাস্তবতায় এ ধরনের একটি আইন দরকার ছিল। আশির দশকে যেসব বিদেশি বিনিয়োগকারী বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়েছিলেন, তারা শ্রমসংক্রান্ত শর্তাবলিকে কিছুটা নমনীয় করার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে বর্তমানে একক শ্রম আইনের অধীনে দেশের সব কারখানা পরিচালিত হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে ইপিজেডের কারখানা মালিকদের কিছুটা অনাগ্রহ থাকতে পারে। তা ছাড়া ইপিজেডের যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে, তাদের দিক থেকে স্বাধীনভাবে চলার একটা প্রবণতা আছে। এসব কারণে ইপিজেড এখনো পৃথকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে প্রচলিত শ্রম আইনের বাইরে গিয়ে। এসব কারণে ইপিজেড আইন ও প্রচলিত শ্রম আইনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়টি এগোয়নি। কিন্তু আশি দশকের বাস্তবতা দেশে বিদ্যমান নেই। কাজেই দেশে এখন কোনো নির্দিষ্ট খাতের জন্য পৃথক শ্রম আইন অপ্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে দেশে ভিন্ন আইন হওয়া উচিত। কেননা তৈরি পোশাকসহ প্রধান প্রধান শিল্প খাতে ইপিজেড ও ইপিজেডের বাইরের কমপ্লায়েন্স বর্তমানে কাছাকাছি পর্যায়ে চলে এসেছে। আইএলও কনভেনশন অনুস্বাক্ষরের বিষয়ে সিপিডি সুপারিশ দিয়েছে। এ ছাড়া শ্রম আইনে ডিজিটাল রিপোর্টিংয়ের যে প্রবিধান রয়েছে, সেটি অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি শ্রম আইনে কর্মক্ষেত্রে জখমের যে তফসিল দেওয়া আছে, তাতে সব ধরনের জখম অন্তর্ভুক্ত হয় না। ফলে শ্রমিকরা নির্দিষ্ট জখমের বিপরীতে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন না। তাই সিপিডির পক্ষ থেকে এই তফসিল পর্যালোচনার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া আইএলওর কনভেনশন অনুযায়ী, কর্মক্ষেত্রে সৃষ্ট রোগের তালিকা হালনাগাদ করতে বলা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে আইনি সংস্কারের প্রস্তাব। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে- বেসরকারি খাতের উদ্যোগে কারখানার পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করা। কারণ শিল্প খাতে সরকারি উদ্যোগে পরিদর্শন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অ্যাক্রেডিটেশন দিয়ে এই পরিদর্শন সম্পন্ন করা সম্ভব। এমন একটি উদ্যোগ শুরুও হয়েছিল। পরে সেটি বন্ধ হয়ে গেছে। বিষয়টি পুনরায় চালু হওয়া দরকার। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রুটিন পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।
এ ছাড়া লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনকে (লিমা) মূলধারার কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। শ্রমসংক্রান্ত সব ধরনের তথ্য-উপাত্ত এই প্ল্যাটফর্মে আনতে হবে। কর্মক্ষেত্রে জখম, কারখানার ডিআরএস কার্যক্রম, কারখানার নিবন্ধন ইত্যাদি বিষয়ে সার্বিক তথ্য এই প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। লিমার মাধ্যমে নিবন্ধন প্রাপ্তি, নিবন্ধন বাতিল অথবা নিবন্ধন অনুমোদন সব ধরনের কার্যক্রমের তথ্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এই প্ল্যাটফর্মে একটি কারখানার সামগ্রিক তথ্য-উপাত্ত থাকবে এবং সেই তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে যেকোনো কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কারখানার তথ্য সংগ্রহ করে তাদের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবে। এ ছাড়া কারখানাগুলোও তাদের উপাত্ত নিয়মিত হালনাগাদ করতে পারবে। পাশাপাশি কারখানাগুলোতে মেডিকেল সেবা নিশ্চিত করতে হবে। যে সেবা সবসময় কারখানায় প্রস্তুত থাকে না। পাশাপাশি পরিদর্শন কার্যক্রমের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডাইফি) বাজেট বাড়াতে হবে। এখন যে বাজেট রয়েছে, তা খুব অপর্যাপ্ত। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তারা সঠিকভাবে মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন ও তদারকি করতে পারে না। এ ছাড়া পরিদর্শনের জন্য পর্যাপ্ত গাড়ি নেই সংস্থাটির। ফলে যেসব কারখানা পরিদর্শন করা হবে, ওইসব কারখানা থেকে গাড়ি পাঠানো হয়। এতে স্বভাবতই পরিদর্শন কার্যক্রম পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হতে পারে। কাজেই কার্যকর পরিদর্শন নিশ্চিত করতে ডাইফিকে ডিজিটাল উপকরণ ও অবকাঠামোগত দিক থেকে আরও বেশি সুসজ্জিত করতে হবে। এ ছাড়া পরিচালনগত বিষয়ে কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে একাডেমিক কারিকুলামে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা। আর কারখানার বিপজ্জনক উপকরণ প্রস্তুত, পরিবহন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত কাঠামো তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে যা নেই। পাশাপাশি আবাসিক এলাকা থেকে রাসায়নিক ও প্লাস্টিক কারখানাগুলোকে স্থানান্তরের সুপারিশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। সিপিডির পক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা পরিসংখ্যানের জন্য একটি জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে কারখানায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো ডেটাবেজ পাওয়া যায় না। সবাই নিজেদের মতো করে ডেটাবেজ তৈরি করছে। এক্ষেত্রে পরোক্ষ পরিসংখ্যান তৈরি হচ্ছে। যেমন কোনো কারখানায় একটি দুর্ঘটনা ঘটল। তার ভিত্তিতে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হলো। সেই খবরের ভিত্তিতে পরিসংখ্যান তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু কারখানায় জখমের ঘটনা ঘটলেই যাতে নির্দিষ্ট কোনো সংস্থা বিষয়টিকে গণনায় রাখতে পারে, সে ধরনের কোনো ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।
জখমের সব ঘটনা গণমাধ্যমে নাও আসতে পারে। কিন্তু তার পরিসংখ্যান অবশ্যই থাকতে হবে। এ ছাড়া ডাইডিফ, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিএসটিআই, ফায়ার সার্ভিস, রাজউক প্রভৃতি সংস্থা বছরব্যাপী যে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে, তার আওতায় কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে। বর্তমানে এ বিষয়ে শুধু একটি সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়। যেখানে কারখানায় জখমের ঘটনার প্রকৃত চিত্র উঠে আসে না। কাজেই এক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট হতে হবে। এর পাশাপাশি কারখানার যেসব নিরাপত্তা সরঞ্জাম বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, সেগুলোর শুল্ক কমাতে হবে। যাতে সহজেই কারখানা কর্তৃপক্ষ সেগুলো আনতে পারে। আর ছোট আকারের কারখানাগুলো যাতে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে পারে, সে জন্য স্বল্প খরচে তহবিল জোগান দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। কারণ এ ধরনের বিনিয়োগের জন্য ব্যাংক ঋণ দিতে চায় না। কারখানা কর্মীদের মাসিক ডেটা হালনাগাদ ও তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। বর্তমানে এ ধরনের কোনো উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয় না। সাধারণত সব কারখানার নিজস্ব একটি ডেটাবেজ আছে। সেটিকেই মাসিকভিত্তিতে ডাইফি এবং শ্রম মন্ত্রণালয়ে অবহিত করতে হবে। এভাবে একটি জাতীয় ডেটাবেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অর্থাৎ কারখানা সম্পর্কিত সামগ্রিক উপাত্ত (দুর্ঘটনা, জখম, শ্রমিক সংখ্যা, উৎপাদন, রপ্তানি ইত্যাদি) একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্মের অধীনে আনতে হবে। যার মাধ্যমে কারখানাগুলো পরিবীক্ষণ ও ট্রাক করার পাশাপাশি, প্রয়োজন মতো পদক্ষেপ নেওয়া যাবে।
লেখক: গবেষণা পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)