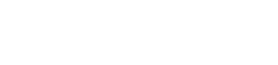Originally posted in খবরের কাগজ on 19 June 2025
বাংলাদেশের আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও প্রত্যাশা পূরণে সাফল্যের বিচারেই ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে বিভিন্ন দিকের মূল্যায়ন সমীচীন ও যৌক্তিক হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়কালে প্রণীত এ বাজেটের মূল দর্শন হওয়ার কথা ছিল বৈষম্য হ্রাস এবং কর্মসৃজনের মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির ভিত রচনা করা, যা পরবর্তীতে রাজনৈতিক সরকারের জন্য একটি পথনির্দেশ রেখে যেতে পারে। বাজেটে প্রস্তাবিত রাজস্ব আয় ও কর কাঠামো, রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয়ের-বিন্যাস, আয় পুনর্বণ্টনের ন্যায্যতা, খাতওয়ারি ব্যয় এবং ও উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রাধিকার নির্ধারণের মাপকাঠিতেই বাজেটকে মূল্যায়ন করা, সে কারণে যুক্তিযুক্ত হবে। আর এসব অর্জন করতে হলে উচ্চমূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগে চাঞ্চল্য আনা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল। জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে এবং বিনিয়োগ-ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বেশ কিছু উদ্যোগের প্রস্তাব থাকলেও বণ্টনের ন্যায্যতা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির বর্তমান চাহিদার নিরীখে প্রস্তাবিত বাজেট গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে ব্যতিক্রমধর্মী হয়েছে, সে কথা বলা যাবে না।
আয়বৈষম্য হ্রাস ও প্রত্যক্ষ কর কাঠামো
গত দুই বছরে গড় মূল্যস্ফীতির উচ্চহারের কারণে ভোগ্যপণ্যের মূল্য ২০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। সে বিবেচনায় করমুক্ত আয়ের সীমা ২০২৫-২৬ করবর্ষের জন্য অপরিবর্তিত রেখে ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ করবর্ষে ২৫ হাজার টাকা মাত্র বৃদ্ধি করা হয়েছে। দুই বছর আগে নির্ধারিত করমুক্ত যে আয়ের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল তার ক্রয়ক্ষমতার অবনমনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আয়কর কাঠামো নিম্ন মধ্যবিত্তের ওপরে বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে। এ সীমা ৪ লাখে নিলে এবং ২০২৫-২৬ করবর্ষ থেকে বাস্তবায়িত হলে তা অধিকতর যুক্তিসম্মত হতো। অন্যদিকে, আয়করের বিভিন্ন স্ল্যাবের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন করা হয়েছে (৫ শতাংশ স্ল্যাব বাতিলের প্রস্তাবের সাপেক্ষে) তা মূল্যস্ফীতির চলমান প্রেক্ষাপটে নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করবে, বিশেষত যখন মজুরি ও আয় পাল্লা দিয়ে বাড়ছে না। যাদের বাৎসরিক আয় ৬ লাখ টাকা বা ১০ লাখ টাকা তাদের আয়কর প্রস্তাবিত করহারের ফলে আগামী দুই করবর্ষে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে ১২.৫ শতাংশ ও ১৬.৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে। যেসব পরিবারের মাসিক আয় ৬০-৭০ হাজার টাকা, ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ করবর্ষের জন্য প্রস্তাবিত কর কাঠামোয় তাদের কর ২০২৫-২৬ অর্থবছরের তুলনায় প্রতি বছর ১১ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু যেসব পরিবারের বাৎসরিক আয় ৩০ লাখ টাকা তাদের কর তুলনামূলকভাবে কম হারে অর্থাৎ ৭.৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে। এটা অবশ্য ইতিবাচক যে, বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য করমুক্ত আয়ের ক্ষেত্রে বাড়তি ছাড় দেওয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ কর হার কোভিড-পূর্ব ৩০ শতাংশের পর্যায়ে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ২০২৫-২৬ করবর্ষ থেকেই কার্যকর হবে। এ প্রস্তাব আয় পুনর্বণ্টনের ন্যায্যতার দিক থেকে যুক্তিযুক্ত হয়েছে তা অবশ্য অনস্বীকার্য।
এটা সুবিদিত যে, আয়বৈষম্য হ্রাসের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কর আদায়ের ওপর জোর দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ করের অণুপাত এক-তৃতীয়াংশ বনাম দুই-তৃতীয়াংশ। অধিকাংশ দেশের ক্ষেত্রেই এটা বিপরীত। এটা প্রত্যাশিত ছিল যে, প্রত্যক্ষ করের ওপর জোর দিয়ে এবং অপ্রত্যক্ষ করের বোঝা না চাপিয়ে কর ভারে সমতা বিধান ও বণ্টনে ন্যায্যতা আনার সচেতন প্রয়াস প্রস্তাবিত বাজেটে পরিলক্ষিত হবে। সর্বোচ্চ কর হার ৩০ শতাংশে নেওয়া এবং সম্পদের সারচার্জ পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে সে লক্ষ্যে একটি চেষ্টা বাজেটে আছে। কিন্তু এসব আগেও ছিল। এসবের অতিরিক্ত পদক্ষেপ হিসেবে সম্পদ কর বা উত্তরাধিকার করের মতো ব্যতিক্রমী উদ্যোগের প্রস্তাব বাজেটে করা হয়নি।
অপ্রত্যক্ষ করকাঠামো ও তার তাৎপর্য
আইএমএফের সঙ্গে ২০২৩ সালে সম্পাদিত ঋণ চুক্তির অধীনে ভ্যাটের হার ১৫ শতাংশের অভিন্ন কাঠামোয় নেওয়ার জন্য সংস্থাটির একটি শর্ত ছিল, যার প্রতিফলন বাজেটের বিভিন্ন প্রস্তাবে দেখা গেছে। বেশ কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে ভ্যাট বৃদ্ধি করা হয়েছে; অনলাইন ব্যবসায় কমিশনের ওপর ভ্যাটের হার ৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে; গৃহস্থালি পণ্যের উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। এগুলো ভোক্তার ওপরই শেষ বিচারে বর্তাবে। যদিও অপ্রত্যক্ষ করকাঠামোর যৌক্তিকরণ ও অ্যান্টি-এক্সপোর্ট বায়াস হ্রাসের লক্ষ্যে বেশ কিছু পণ্যে আমদানি শুল্কহার হ্রাস করা হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ ও ট্রাম্পের পাল্টাপাল্টি শুল্কের পরিপ্রেক্ষিতে পদক্ষেপ গ্রহণও এ ক্ষেত্রে একটি ভূমিকা রেখেছে। বাজেটে ন্যূনতম মূল্য ও ট্যারিফ মূল্য প্রত্যাহারের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে এবং কয়েকটি পণ্যের ন্যূনতম মূল্য হ্রাস করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে আবার কয়েকটি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিও করা হয়েছে, যার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।
শুল্ককাঠামো ও সম্পূরক শুল্কের ক্ষেত্রে বাড়তি আরও একটি স্তর যোগ করা হয়েছে। আমদানিপণ্যের ওপর শুল্কের পুনর্বিন্যাস কোন কোন বিবেচনায় নির্ধারণ করা হয়েছে তার ক্ষেত্রে স্পষ্টতা থাকা উচিত ছিল। আমদানি প্রতিস্থাপক, শিল্পের সুরক্ষা, অ্যান্টি-এক্সপোর্ট বায়াস হ্রাস বা অন্য যেসব বিবেচনা শুল্কহার বিন্যাসের ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা হিসেবে কাজ করেছে তা স্বচ্ছতার সঙ্গে উপস্থাপন করা উচিত ছিল। বাণিজ্যনীতি ও শিল্পনীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন ও আমদানি শুল্ক, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ককাঠামো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে স্থানীয় এবং আমদানি প্রতিস্থাপক শিল্প খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার ওপর তার প্রভাব কতটা বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে তাও স্পষ্ট নয়। ফলে, স্থানীয় শিল্প আমদানিকৃত পণ্যের সঙ্গে আরও বেশি অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
রাজস্ব ব্যবস্থাপনা
কর আদায় বৃদ্ধি, সহজভাবে কর আদায়ের সুবিধার্থে এবং কর ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা মোকাবিলা করতে গিয়ে অগ্রিম আয়কর, অগ্রিম ভ্যাট ইত্যাদিসহ উৎসে কর কর্তনের ওপর বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা বিগত সময়ে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রচলিত ধারা থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট বের হতে পারেনি। অনেক পণ্যে নতুন করে দুই শতাংশ হারে অগ্রিম আয়কর আরোপ করা হয়েছে। বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের ক্ষেত্রে আগাম কর ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ করা হয়েছে, যদিও এটাকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ধরে নেওয়া হবে বলা হয়েছে। জানা কথা, পরবর্তীতে প্রদেয় করের সঙ্গে অগ্রীম করের সমন্বয় করার ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হয়। যদিও এবার বেশ কিছু ক্ষেত্রে অগ্রিম ভ্যাটকে চূড়ান্ত হিসেবে ধরা হয়েছে, এবং কিছু ক্ষেত্রে সমন্বয়ের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। সমস্যা হলো, এ ধরনের অগ্রিম আয়কর অনেক ব্যবসায়ী বিক্রয় কর হিসেবে বিবেচনা করেন এবং ভোক্তার ওপরে চাপিয়ে দেন। এটা আয়কর আরোপের নীতিমালা ও দর্শনের পরিপন্থি। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে ভ্যাটের হার যা অনেকক্ষেত্রেই সেলস ট্যাক্স (বিক্রয় কর)-এর মতোই কাজ করে, সে ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশে নির্ধারণ করে অভিন্নভাবে প্রয়োগ করা কতটা যুক্তিসংগত তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। বাজেটে ভ্যাটহার কিছুটা নামিয়ে (যেমন ১০ শতাংশ) সমভাবে প্রয়োগের দিকে গেলে ভ্যাট বাস্তবায়ন সহজতর হতো এবং ভ্যাট কার্যক্রমে গতিশীলতা নিয়ে আসাও সম্ভব হতো। এটা মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশে যত পয়েন্টে ভ্যাট আদায় করা হয়, সরকারের কোষাগারে তার একটি অংশ মাত্র যোগ হয়। ৩ লাখ ইএফডি মেশিন স্থাপনের পরিকল্পনা থেকে রাজস্ব কর্তৃপক্ষ সরে এল কি না তাও বোধগম্য নয়। জরিমানা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও বেশ কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যদিয়ে বাস্তবতার পরিবর্তন নয়, বাস্তবতা মেনে নেওয়ার দিকেই বেশি ঝোঁক দৃশ্যমান বলে প্রতীয়মান হয়।
রাজস্বকাঠামো ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিনির্ভর নিয়মনীতির মাধ্যমে নির্ধারিত ও পরিচালিত হওয়ার কথা। কিন্তু অতীতে এ ক্ষেত্রে অনেক ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে। দেখা গেছে, ব্যক্তিস্বার্থ এবং কোম্পানিস্বার্থকে বিবেচনায় নিয়ে অনেক ক্ষেত্রে আয়কর ও করপোরেট করের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এবার অবশ্য সে ধরনের প্রবণতা বাজেটে নেই, যা ইতিবাচক ও অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে এটাই প্রত্যাশিত ছিল। করপোরেট করের ক্ষেত্রে পুঁজিবাজারে লিস্টেড ও নন-লিস্টেড কোম্পানির মধ্যে করপোরেট করহারের পার্থক্য বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সব ধরনের আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করলে বাড়তি সুবিধার কথা বলা হয়েছে। মার্চেন্ট ব্যাংকের কর হার ১০ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছে। এসব প্রস্তাব ইতিবাচক। তবে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, পুঁজিবাজের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা না গেলে এবং বিনিয়োগকারী ও ব্যক্তি খাতের মালিকানাধীন ভালো কোম্পানির আস্থা অর্জন করতে সক্ষম না হলে কেবলমাত্র কর হারের পরিবর্তন করে স্থবির পুঁজিবাজারকে চাঙা করা যাবে না ও বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করা সম্ভব হবে না। এসব ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন কী হয়েছে বা পুঁজিবাজার সংস্কার কমিটির সুপারিশ কীভাবে বাস্তবায়িত হবে তা বিস্তারিত ব্যাখ্যার দারি রাখে। বাজেটে এসব বিষয়ে তেমন কিছু বলা হয়নি।
সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়ারহাউস প্রতিষ্ঠাসহ বন্ডেড ওয়ারহাউসের সুবিধার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা রপ্তানিকারকদের জন্য সুবিধাজনক হবে। এটা ভালো প্রস্তাব, কিন্তু এ ক্ষেত্রে বন্ড ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নে আরও নজরদারি করতে হবে এবং বন্ড ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে হবে, যাতে এ সম্প্রসারিত সুযোগ বড় রাজস্ব ক্ষতির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। নিরীক্ষণ শক্তিশালী করার জন্য ডিজিটাল মনিটরিং শক্তিশালী করতে হবে।
প্রণোদনা, ভর্তুকি ইত্যাদির সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন অস্বীকার করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে সানসেট ক্লজ (কখন এসব ছাড় বা প্রণোদনা প্রত্যাহার করা হবে) আরও স্বচ্ছতার সঙ্গে উপস্থাপন করাও প্রয়োজন। বাজেটের প্রস্তাবনাগুলোর কারণে কর ব্যয় কত হ্রাস পাবে তা হিসাব করলে বাজেটের স্বচ্ছতা আরও বৃদ্ধি পেত। বাজেটে উল্লিখিত ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ছাড়ের পরিমাণ মোট জিডিপির ২.৩৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে প্রস্তাবিত কর কাঠামোয় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কত দাঁড়াবে তার একটা হিসাব উপস্থাপন করা প্রয়োজন ছিল
করজাল সম্প্রসারণ
রাজস্ব বাজেটের আয়ের ভিত্তি ও করজালের সম্প্রসারণ, নতুন রাজস্বের উৎস শনাক্তকরণ ও কর ফাঁকির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতার সুযোগ ছিল এ বছরই। কিন্তু বাজেটে গতানুগতিকভাবে আমদানি কর, ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক ইত্যাদির সুবাদে ও আয়কর বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের প্রচলিত ধারাই আব্যাহত আছে। তবে এটা ইতিবাচক যে, আইটি এনাবল্ড সেবা খাত, যেমন- ই-কমার্স ও এফ-কমার্সকে করজালে আনার একটা প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। জানা কথা, জনসাধারণ যে কর-রাজস্ব দিয়ে থাকেন তার একটা বড় অংশ সরকারের কোষাগাড়ে জমা পড়ে না। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আন্ডার-ওভার ইনভয়েসিং, কর প্রদানের ক্ষেত্রে করজালে না থাকা এবং কর ফাঁকি ও কর পরিহার এবং রাজস্ব খাতে দুর্নীতির কারণে বড় ধরনের রাজস্ব ক্ষতি হয়ে থাকে। কর ব্যবস্থাপনায় সংস্কার করে ও তাকে যুগোপযোগী করে, প্রযুক্তিকে আরও ব্যাপক পরিসরে ও দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করে এবং ব্যয় ও আয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ‘আধার কার্ড’-এর অনুরূপ ব্যবস্থা চালু করে বাড়তি কর আহরণের মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য যে উদ্যোগ-উদ্যম প্রয়োজন ছিল ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে সে ধরনের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির উল্লেখ নেই। নতুন কতজনকে করজালে আনা হবে, কর ফাঁকি রোধ করে ও প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলো থেকে কত বাড়তি রাজস্ব আয় আসবে বলে প্রাক্কলন করা হচ্ছে, তার ধারণা বাজেট থেকে পাওয়া যায় না। আয়বৈষম্য, ভোগবৈষম্য ও সম্পদবৈষম্য কী পরিমাণে হ্রাস পাবে, বাজেট থেকে সে সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া কষ্টকর।
মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়োগে ত্বরণ সৃষ্টি
২০২২ সালে রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর বাংলাদেশের উচ্চমূল্যস্ফীতির ধারাবাহিকতা তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাম্প্রতিক সময়ে প্রবাসী আয়ে চাঙাভাব ও ভালো রপ্তানি আয়ের সুবাদে রিজার্ভের অব্যাহত পতন রোধ করা সম্ভব হয়েছে। আমদানিতে কিছুটা গতি এসেছে। ফলে, আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে যা সার্বিক মূল্যস্ফীতির হারকে কিছুটা হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। এসব ইতিবাচক, কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে, উচ্চমূল্যস্ফীতির কারণে মূল্যস্তর বর্তমানে বেশ উঁচুতে অবস্থান করছে। মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হলে বিনিয়োগকে চাঙা করতে হবে, যার মাধ্যমে একদিকে সরবরাহে গতি আসবে অন্যদিকে শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে শ্রমবাজারে অন্তর্ভুক্ত বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে কিছু বিষয় আছে, যেগুলো বাজেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, অন্যগুলো বাজেটের বাইরে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষতার সঙ্গে জড়িত এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর এবং নির্বাচন নিয়ে নিশ্চয়তা-অনিশ্চয়তার ওপরও অনেকাংশে নির্ভরশীল।
বিদ্যুৎ-জ্বালানির ভর্তুকি হ্রাস ও এসবের মূল্যবৃদ্ধি বাজেটের আগেই করা হয়েছে। অতীতের পুঞ্জীভূত দুর্নীতি, অনিয়ম ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতা বিনিয়োগকারীদের এবং ভোক্তামহলকে বহন করতে হচ্ছে চড়া দামে বিদ্যুৎ-গ্যাস ক্রয়ের বাধ্যবাধকতায়। উচ্চ সুদহার, বিদ্যুৎ-জ্বালানির উচ্চমূল্য, গ্যাসের প্রাপ্যতায় সমস্যা, টাকার বড় ধরনের অবমূল্যায়ন ও উচ্চমূল্যস্ফীতিকে বাজেটের মাধ্যমে প্রাপ্য বাড়তি সুবিধার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন, এমন আশা বাজেট দেখাতে পারেনি। তবে ব্যক্তি খাত ও বিনিয়োগে চাঞ্চল্য শেষের বিচারে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার গুণগত মান, উন্নত বিনিয়োগ পরিবেশ ও বিনিয়োগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যয় হ্রাসের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুঘটকের ওপরই বেশি নির্ভর করবে।
সামাজিক সুরক্ষা ও কর্মসৃজন
প্রান্তিক জনসাধারণের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নিকট অতীতে উচ্চমূল্যস্ফীতির কারণে এ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতার ধারাবাহিক অবনমন হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির কিছু কাঠামোগত সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং ভিত্তি ও প্রাপ্তির সম্প্রসারণে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা ইতিবাচক। এটা বর্তমানে বিশেষভাবে জরুরি এ কারণে যে, সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় ৩০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাওয়ার আশঙ্কায় আছে উচ্চমূল্যস্ফীতির চাপের কারণে। বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষার অধীনে প্রাপ্তি ও ভাতার ক্রয়ক্ষমতাও এসব কারণে হ্রাস পেয়েছে। শহরাঞ্চলে যেহেতু সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি নেই বললেই চলে, সে কারণে প্রয়োজন ছিল শ্রমিকদের জন্য রেশনিং সুবিধা চালু করার মতো পদক্ষেপ। কিন্তু বাজেটে সে ধরনের উদ্যোগ নেই। শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে শ্রমিক ঘনবসতি এলাকায়, খোলা বাজারে বিক্রয়ের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমেও শ্রমিকদের কিছুটা স্বস্তি দেওয়া যেতে পারে।
অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি বিনির্মাণের পূর্বশর্ত হলো শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে শোভন আয়ের সুযোগ সৃষ্টি। সুবিদিত যে, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, বিশেষত শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের জন্য বর্ধিত হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ছিল জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের অন্যতম দাবি। শিক্ষা-প্রশিক্ষণ-কর্ম জগতের বাইরে বিশাল এক জনগোষ্ঠী আছে যাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি উন্নয়নের একটি মূল দর্শন হওয়ার কথা ছিল। লেবার ফোর্স সার্ভে থেকে দেখা যাচ্ছে, চলমান অর্থবছরে প্রথম ছয় মাস বেকারের সংখ্যা ২১ লাখ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার বড় অংশই নারী। পুরাতন ও নতুন বেকারের জন্য লক্ষ্যনির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ ও ব্যক্তি খাতকে অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশের নিশ্চয়তা দেওয়ার মাধ্যমেই এ সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব। বাজেটে লক্ষ্যনির্দিষ্টভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়ার প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিশেষত শিক্ষিত যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব বাজেটে নেই। কর্মসংস্থান সমস্যার সমাধান রাজস্বনীতি, আর্থিকনীতি ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ত্রিমাত্রিক কার্যকর সংশ্লেষের মাধ্যমেই সম্ভবপর হবে। বাজেটে এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি নিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব থাকলে এ ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যেত।
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
এবার যেহেতু আকার নয়, উন্নয়ন প্রকল্প যাচাই-বাছাই ও চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়নকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, সেহেতু সাশ্রয়ীভাবে ও সুশাসনের সঙ্গে প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও সময়মতো প্রকল্প শেষ করার ক্ষেত্রে অধিকতর মনোযোগী হতে হবে। অতীতে অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ও বিশেষ গোষ্ঠীস্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প নির্বাচন ও অতিমূল্যায়িত বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামীতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেটের আকার কিছুটা ছোট রেখে তারই ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের সুফল নির্ভর করবে সব পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সাশ্রয়ীভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সময়মতো প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার ওপর। এগুলোর প্রয়োজনীয়তা ২০২৫-২৬ অর্থছরে অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় আরও জরুরি হয়ে দাঁড়াবে।
বাজেটের আকার ও ঋণনির্ভরতা
রাজস্ব বাজেটে উদ্বৃত্ত না থাকার কারণে বাংলাদেশের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সম্পূর্ণটাই অব্যাহতভাবে ঋণনির্ভর থেকে গেছে। রাজস্ব আয় ৫ লাখ ৬৪ হাজার কোটি টাকা আর রাজস্ব ব্যয় ৫ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকা। আদায়কৃত রাজস্বের একটি উল্ল্যেখযোগ্য অংশ চলে যাচ্ছে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধে, যদিও রাজস্ব ব্যয়ে কেবলমাত্র ঋণ পরিশোধে সুদের অংশই দেখানো হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে ঋণ সুদ-ব্যয় শিক্ষাকে ছাড়িয়ে রাজস্ব ব্যয়ের দ্বিতীয় প্রধানতম খাত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটেও এ প্রবণতা অব্যাহত আছে।
কর জিডিপির হার ৮-৯ শতাংশের মধ্যে থাকলে, তার সঙ্গে ঘাটতি অর্থায়ন জিডিপির হার ৪-৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হলে, বাংলাদেশের সরকারি ব্যয় জিডিপির হার ১৩-১৪ শতাংশের বেশি করা যাবে না। উন্নয়নশীল বিশ্ব ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের রাজস্ব-জিডিপির হার অন্যতম সর্বনিম্ন। প্রতিবেশী দেশ ভারত ও নেপালে এ হার ২৪ শতাংশের বেশি। অনেক উন্নত দেশে এ হার ৩০-৪০ শতাংশ। সুতরাং ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে সরকারি ব্যয়ের যে আকার প্রস্তাব করা হয়েছে উদ্যম-উদ্যোগ-কর্মসূচি গ্রহণের নিরীখে তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং তার থেকে বেশি প্রত্যাশা করা অনুচিতই হবে। দুঃখের বিষয় হলো, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট বহুদিনের দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে আসার পথ দেখাতে পারেনি। মধ্যম আয় এবং এলডিসি থেকে উত্তরকালীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য কর ও রাজস্ব-জিডিপির নিম্ন হার একবিংশ শতাব্দীতে চলার পথে অনতিক্রম্য বাধা হয়ে দাঁড়াবে। বরং অপ্রত্যাশিত অর্থ সাদা করার সুবিধা অব্যাহত রেখে জুলাই-আগস্ট আন্দোলন-সংগ্রামের মূল চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং আন্দোলনের মূল আকাঙ্ক্ষার প্রতি যথার্থ ন্যায়বিচার করা হয়নি।
শেষ কথা
প্রয়োজন ছিল গতানুগতিকতার বেড়াজাল থেকে বেড়িয়ে এসে ভিন্নধর্মী চিন্তার ও উদ্ভাবনী ভাবনার আলোকে নতুন ধারার বাজেট উপস্থাপন। পরিতাপের বিষয়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট সেদিক থেকে আশাহতই করেছে।
লেখক: অধ্যাপক, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি