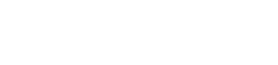Originally posted in বণিক বার্তা on 2 February 2025
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কমানোর সুপারিশ টাস্কফোর্সের
একীভূতকরণের মাধ্যমে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কমানোর সুপারিশ করেছে সরকার গঠিত বৈষম্যহীন টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণবিষয়ক টাস্কফোর্স।

একীভূতকরণের মাধ্যমে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কমানোর সুপারিশ করেছে সরকার গঠিত বৈষম্যহীন টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণবিষয়ক টাস্কফোর্স। সীমিত শিক্ষা বাজেটের সঠিক ব্যবহার ও আন্তর্জাতিক র্যাংকিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভালো অবস্থান নিশ্চিতে এ কৌশল নেয়া যেতে পারে বলে মনে করছেন টাস্কফোর্সের সদস্যরা। টাস্কফোর্স কমিটির পক্ষ থেকে এ সুপারিশ সংবলিত একটি প্রতিবেদন গত বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সীমিত শিক্ষা বাজেটের সঠিক ব্যবহার, সম্পদ ভাগাভাগির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক র্যাংকিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভালো অবস্থান নিশ্চিতে সরকারের উচিত কিছু পাবলিক ও কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে একীভূত করার বিষয়টি বিবেচনা করা।
টাস্কফোর্সের শিক্ষাবিষয়ক সুপারিশগুলো তৈরিতে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, ‘আমাদের দেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই নিম্নমানসম্পন্ন। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতে এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতের উদ্দেশ্যেই এ একীভূতকরণের সুপারিশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এবং কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত করা যেতে পারে। তবে একীভূতকরণের অর্থ এই নয় যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাবে। তাদের ক্যাম্পাস আগের জায়গায়ই থাকবে। তবে তারা একই নামে পরিচালিত হবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে সরকারই একীভূতকরণের উদ্যোগ নিতে পারে। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে একটি ন্যূনতম মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিতে পারে, যা তাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্জন করতে হবে। যদি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এ সময়ের মধ্যে মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের একীভূতকরণের পদক্ষেপ নিতে হবে।’
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৭০। এর মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ৫৫টি। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১১৫টি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অর্ধেকেরও বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ১৫ বছরে। ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী, এ দেড় দশকে মোট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৮৭টি। এর মধ্যে ২৬টি পাবলিক ও ৬১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।
আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ সময়ে নতুন করে আরো ১০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সাতক্ষীরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, লক্ষ্মীপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন গত বছর সংসদে পাস হয়েছে। ড. এমএ ওয়াজেদ মিয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের খসড়াও একই বছর সংসদে চূড়ান্ত হয়। বাকি ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে ইউজিসি ইতিবাচক মতামত দিয়েছিল।
সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, দেশে ছয় বছরের ব্যবধানে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে। শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৩-এ উঠে আসা এ তথ্য অনুযায়ী, দেশে উচ্চশিক্ষিত অর্থাৎ স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী বেকারের সংখ্যা ৯ লাখ ৬ হাজার। এর আগে ২০১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপে ৪ লাখ ৫ হাজার জন উচ্চশিক্ষিত বেকারের তথ্য উঠে এসেছিল। সে হিসেবে ছয় বছরের ব্যবধানে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৫ লাখ ৪ হাজার। শিক্ষাসংশ্লিষ্টদের মতে মান নিশ্চিত না করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাই উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্ব বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য এবং বিডিজবসডটকমের সিইও একেএম ফাহিম মাশরুর বণিক বার্তাকে বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমরা গুণগত মান নিশ্চিত করতে পারছি না। ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা অনুযায়ী তা পরিপূর্ণ হচ্ছে না। এ জায়গায় বিনিয়োগ তো অনেক হয়েছে। সরকারও অনেক বেশি পরিমাণে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে ফেলেছে। এত বিশ্ববিদ্যালয়ের তো দরকার আছে বলে মনে হয় না। সংখ্যার বাইরে গিয়ে এখন গুণগত মানে ফোকাস করা দরকার। এক্ষেত্রে সংখ্যায় কমিয়ে হলেও গুণগত মান নিশ্চিত করাটা গুরুত্বপূর্ণ।’
শিক্ষাসংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, বিগত ১৫ বছরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেশের শ্রমবাজারের চাহিদা বা শিক্ষার মানের পরিবর্তে রাজনৈতিক বিবেচনা প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। বিশেষত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দলীয় বিবেচনা অধিক গুরুত্ব পেয়েছে।
ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, এ দেড় দশকে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অধিকাংশেরই পর্যাপ্ত শিক্ষক, নিজস্ব ক্যাম্পাস, আবাসন ও ল্যাবসহ প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নেই। নিয়ম অনুযায়ী, উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আদর্শ অনুপাত বিবেচনায় প্রতি ২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য অন্তত একজন শিক্ষক থাকার কথা। কিন্তু দেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আদর্শ অনুপাত বজায় নেই ৬৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর মধ্যে ১৮টি পাবলিক ও ৪৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।
এছাড়া ইউজিসির নীতিমালা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের প্রতিটি প্রোগ্রামে ন্যূনতম একজন অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক থাকা বাধ্যতামূলক। যদিও দেশের ১৩টি পাবলিক ও ৬০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এ শর্ত পূরণ করতে পারছে না। এমনকি কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় চলছে কোনো অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক ছাড়াই। দেশের সাতটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং নয়টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন পরিস্থিতি দেখা যায়।
এ বিষয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান বণিক বার্তাকে বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি। তবে বর্তমানে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নেই। এর ফলে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিষয়গুলো বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নয়নে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়কে একীভূত করার সুপারিশটি ইতিবাচক। এটি করা হলে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাবসহ বিভিন্ন সংকট রয়েছে, সেগুলোর শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাজেট; বিশেষ করে গবেষণা খাতে বরাদ্দ আরো অনেক বাড়ানো প্রয়োজন।’
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পর্যাপ্ত পরিমাণ বাজেট না পাওয়ার এ অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই উঠছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের ৫৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেট দেয়া হয়েছে ১১ হাজার ৬৯০ কোটি ৪ লাখ টাকার। এর মধ্যে গবেষণা খাতে বরাদ্দ ১৮৮ কোটি ৬৫ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ পেয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টির জন্য মোট বরাদ্দ ৮০৪ কোটি ৪১ লাখ টাকা। আর গবেষণা খাতে বরাদ্দ ২০ কোটি টাকা।
দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের আবাসনসহ প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার কথা। যদিও বর্তমানে দেশের ৫৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২১টিরই নিজস্ব ক্যাম্পাস নেই। এগুলোর মধ্যে ১৭টির জন্য এখনো কোনো ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়নি। এসব বিশ্ববিদ্যালয় ভাড়া ভবন বা অস্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সংকটের জেরে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় ক্লাসরুম, ল্যাব, লাইব্রেরি এবং আবাসন সুবিধার মতো মৌলিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এমনকি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, প্রকৌশল ও কৃষিসংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোও পরিচালিত হচ্ছে প্রয়োজনীয় ল্যাব সুবিধা ছাড়া।
বর্তমানে দেশের ২১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আবাসন সুবিধা ৩০ শতাংশের নিচে। অর্থাৎ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি শিক্ষার্থী আবাসন সুবিধা পাচ্ছে না। অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে না পারলে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে কাঙ্ক্ষিত সুফল মিলবে না বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের অধ্যাপক প্রফেসর ড. মো. আব্দুস সালাম বণিক বার্তাকে বলেন, ‘আমাদের যেটি প্রয়োজন সেটি হলো মেধাবীদের জন্য মানসম্মত উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা। বিগত বছরগুলোয় শিক্ষক ও অবকাঠামো ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করায় উচ্চশিক্ষার মানের মারাত্মক অবনমন ঘটেছে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই এ মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এবং দক্ষ শিক্ষকসহ মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত না করতে পারলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাষ্ট্রকে লাভবান করতে পারবে না।’
দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৭৮টির স্থায়ী ক্যাম্পাস নেই। যদিও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠার সাত বছরের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার নিয়ম রয়েছে। স্থায়ী ক্যাম্পাসবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সাত বছরের বেশি সময় আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৬। এ ৫৬টির মধ্যে বেশির ভাগেই ক্লাসরুম, ল্যাব ও লাইব্রেরি সুবিধার ঘাটতি রয়েছে।
মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে না পারলে সার্বিক মানে পিছিয়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রাষ্ট্রের বোঝায় পরিণত হবে বলে মনে করছেন ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (আইইউবি) উপাচার্য অধ্যাপক ম. তামিম। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, ‘আমাদের দেশে এমন বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যাদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নেই। বিশেষত তুলনামূলক নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে দক্ষ শিক্ষকসহ প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার বেশ ঘাটতি রয়েছে। ফলে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে না এবং শিক্ষার্থীরা কর্মজীবনে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাচ্ছে না। দেশে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে রাষ্ট্রের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হলে অবশ্যই মানসম্মত শিক্ষা ও কার্যকর গবেষণার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় একীভূতকরণ জটিল প্রক্রিয়া। কোন উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একীভূত করা যেতে পারে, সে বিষয়েও একটি নীতি সুপারিশের প্রয়োজন ছিল। সরকার যদি এ সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়, তবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়তো তুলনামূলক সহজে একীভূত করা যাবে। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে মালিকানাসহ বিভিন্ন বিষয় রয়েছে।’
টাস্কফোর্সের সুপারিশের বিষয়ে জানতে চাইলে ইউজিসির সদস্য ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান বণিক বার্তাকে বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়কে অবশ্যই মানসম্মত হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল বা কিন্ডারগার্টেনের মতো হলে রাষ্ট্র লাভবান হবে না। আমাদের দেশে গত ১৫ বছরে রাজনৈতিক বিবেচনায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলোর বেশির ভাগের অবস্থাই ভালো নয়। ২৬টি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২১টিই চলছে ভাড়া বা অস্থায়ী ক্যাম্পাসে। আমরা চেষ্টা করছি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন সংকট সমাধানের। তবে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এমন অবস্থায় আছে, যেগুলোর সংকট সমাধান সম্ভব নয়। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা একেবারেই সমাধান সম্ভব নয়, সেগুলোর বিষয়ে আমাদের অবশ্যই বিকল্প চিন্তা করতে হবে।’